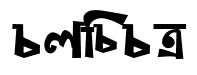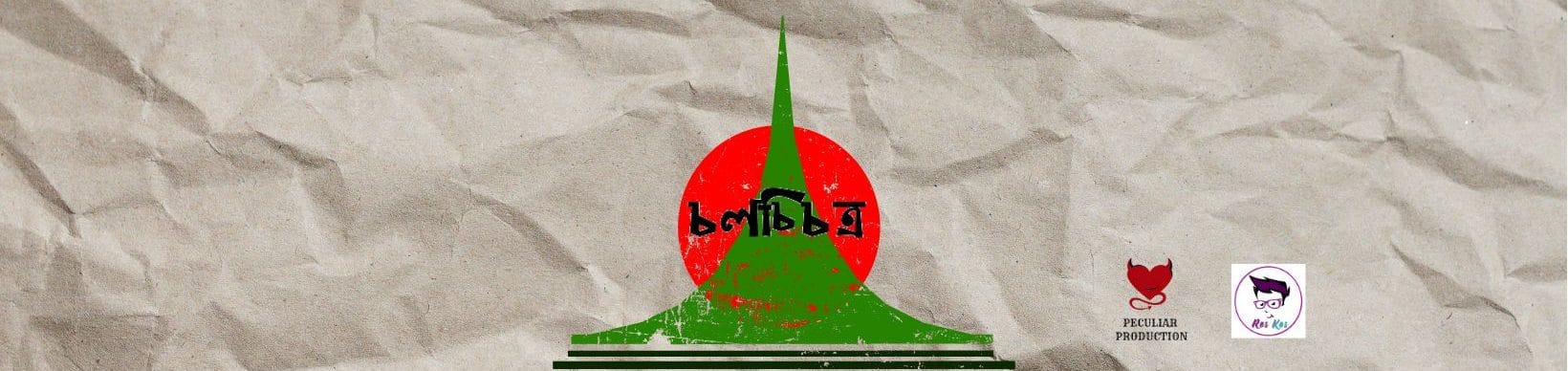১৭১৯ সালে রবিনসন ক্রুসো উপন্যাসটি প্রকাশের পরেই সাড়া পড়ে যায় গোটা ব্রিটেন জুড়ে এবং বইটির একের পর এক সংস্করণ হতে থাকে। জনপ্রিয় সংবাদপত্রেও পর্বে পর্বে এর পুনঃপ্রকাশ হয়। প্রকাশিত হতে শুরু করে এই ধাঁচের আরো অনেক লেখা, যেখানে নায়কের জাহাজডুবি হচ্ছে বা তিনি জলদস্যুদের কবলে পড়ছেন, আর তারপর বছরের পর বছর কাটাতে বাধ্য হচ্ছেন কোনও নির্জন দ্বীপে। শুধুমাত্র সমকালীন ব্রিটেনের গল্পবুভুক্ষু পাঠকের মনই যে রবিনসন ক্রুসো জয় করে নিয়েছিল তা নয়, সেদিনের অষ্টাদশ থেকে আজকের একুশ শতকের ধীমান পাঠক, সমালোচক, দার্শনিক, অর্থনীতিবেত্তারাও বইটি পড়েছেন, তা নিয়ে নানা দৃষ্টিকোণ থেকে আলোচনা করেছেন।
আমরা জানি রুশো একেবারেই পছন্দ করতেন না বিধিবদ্ধ পাঠক্রমকে। এমিলের মতো তাঁর মানসপুত্ররা কেবল প্রকৃতি থেকেই শিখবে, এই ছিল তাঁর ভাবনা। কিন্তু রুশো যে একটিমাত্র বইকে শেষপর্যন্ত এমিলের পাঠ্যতালিকায় রেখেছিলেন, সেটি হল এই রবিনসন ক্রুসো। রবিনসন ক্রুসো এক নির্জন দ্বীপে আটকা পড়ার পর যেভাবে কঠোর পরিশ্রম করে নিজের প্রয়োজনীয় সব কাজ নিজের হাতে করে নিতে শিখেছিলেন, যার মধ্যে ছিল অল্পবিস্তর ফসল ফলানো, খাদ্যের জন্য পশুপালন, নিজের পরিচ্ছদ থেকে জুতো নিজেই তৈরি করা বা থাকার মতো বাড়ি বানিয়ে নেওয়া – সেটাই ছিল রুশোর মতে প্রকৃত শিক্ষা।
অষ্টাদশ শতকের শ্রেষ্ঠ দার্শনিকদের অন্যতম রুশো যেমন ক্রুসোর প্রভাবকে এড়াতে পারেন নি, তেমনি পারেন নি উনিশ শতকের অন্যতম শ্রেষ্ঠ দার্শনিক কার্ল মার্কসও। রিকার্ডো এবং স্মিথের অর্থনৈতিক তত্ত্বের সমালোচনা করেছিলেন কার্ল মার্কস এবং হাজির করেছিলেন সামাজিক উৎপাদনের ক্ষেত্রে শ্রমের ভূমিকার তত্ত্ব। রবিনসন ক্রুসোর উদাহরণটিকে তিনি এনেছিলেন তাঁর বিখ্যাত ক্যাপিটাল বইয়ের প্রথম খণ্ডে। বলেছিলেন রবিনসন ক্রুসোর উৎপাদন একেবারেই ব্যক্তির জন্য কিন্তু সমাজভুক্ত মানুষ যে শ্রম করে, সেই শ্রমের উদ্দেশ্য সামাজিক ভাবে প্রয়োজনীয় পণ্য ও পরিষেবার উৎপাদন।
বিশ শতকের প্রথমার্ধে ইয়ান আয়াট যখন উপন্যাস নামক সাহিত্যবর্গটির বিকাশ প্রতিষ্ঠার কথা লিখলেন সেখানে ড্যানিয়েল ডিফো ও তাঁর চিরায়ত সৃষ্টি রবিনসন ক্রুসো হয়ে উঠল অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য এক অবলম্বন। ইয়ান আয়াট সহ উপন্যাসের ইতিহাসকার ও সাহিত্যবেত্তারা দেখিয়েছেন পুঁজিবাদী সমাজ ও বুর্জোয়া সমাজের বিকাশ প্রতিষ্ঠার সঙ্গে উপন্যাসের মতো আধুনিক সাহিত্য সংরূপের বিকাশ প্রতিষ্ঠার সরাসরি সম্পর্কে আছে। যে সমস্ত আখ্যান এই সম্পর্কসূত্রটিকে বুঝতে আমাদের সাহায্য করে রবিনসন ক্রুসো তার অন্যতম। ডিফোর রবিনসন ক্রুসো খালি জমিতে ফসল ফলানো, পশুর সংখ্যা বিস্তার, শূন্য দ্বীপকে বসবাসযোগ্য করে সম্পদের বিস্তার ঘটানোর যে সব উদাহরণ তৈরি করে, তা পুঁজিবাদী বিকাশের পথে এক জরুরী পদক্ষেপ।
১৬৩২ সালে রবিনসন ক্রুসোর জন্ম বলে আখ্যানকার জানিয়েছেন। সপ্তদশ শতকের ঠিক মাঝামাঝি শুরু হচ্ছে তার অভিযাত্রী জীবন। পূর্ববর্তী ষোড়শ শতক থেকেই স্পেন আর পর্তুগাল আমেরিকায় একের পর এক অভিযান চালিয়েছে। গোটা আমেরিকা মহাদেশকে লুঠ করে তার সম্পদ এনেছে ইউরোপে। সম্পদ লুঠের জন্য শ্রমিক সংগ্রহ করেছে আফ্রিকা থেকে। ক্রীতদাস হিসেবে আফ্রিকার কালো মানুষদের বন্দী করতে ও তাদের নিয়ে আমেরিকার নানা অঞ্চলে ছেড়ে আসতে কাজ করেছে শয়ে শয়ে ইউরোপীয় জাহাজ ও হাজার হাজার নাবিক ও সেনা। পশ্চিমে আমেরিকা ছাড়াও আফ্রিকা ঘুরে পুবে এশিয়াতে আসার জলপথ তারা বের করে ফেলেছে। পুবমুখী অভিযানগুলো চালানোর জন্য ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী তৈরি হয়েছে ১৬০০ খ্রিস্টাব্দে। একইভাবে তৈরি হয়েছে ফরাসী, ডাচ ও নানা ইউরোপীয় দেশের ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীগুলি। পঞ্চদশ শতকের প্রথমার্ধ থেকেই পর্তুগীজরা ভারতে বারেবারে আসতে থাকে। তারা পৌঁছে যাচ্ছিল ইন্দোনেশিয়া সহ দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার দূরতর প্রান্তেও। তারপর ডাচরাও এ পথে আনাগোনা শুরু করে। দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় বাণিজ্যের নিয়ন্ত্রণ অনেকটাই তাদের করায়ত্ত হয়। সপ্তদশ শতকে যখন রবিনসন ক্রুসোর জন্ম ও বড় হয়ে ওঠা, সেই সময়ে ব্রিটিশ, ফরাসী, ডাচ, দিনেমার, স্প্যানিশ, পর্তুগীজ ইত্যাদি নানা ইউরোপীয় শক্তির একের পর নৌ অভিযান চলছে বিশ্বজুড়ে। এই অভিযানগুলি যে মনস্তাত্ত্বিক উন্মাদনা তৈরি করত কিশোর ও যুবক মনে, তার প্রমাণ রবিনসন ক্রুসোর জাহাজী হবার ইচ্ছের মধ্যে ধরা পড়েছে।
“আমার বাবা প্রাচীনপন্থী মানুষ। আমাকে পড়াশোনা যতটা শেখানো সম্ভব শিখিয়েছেন। প্রথমাবস্থায় বাড়িতে, পরে স্থানীয় অবৈতনিক বিদ্যালয়ে। শেষ অব্দি আইন নিয়ে আমি পড়াশুনা করি। কিন্তু পড়ায় মোটে মন লাগে না আমার। সমুদ্র আমাকে টানে, ডাকে। যেতে ইচ্ছে করে সমুদ্রে। সারাক্ষণ মনের আনাচে কানাচে তোলপাড় করে বেড়ায় ভাবনা। শেষে অবস্থা এমন পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছল, বাবার বিরুদ্ধতা পর্যন্ত করতে বাধ্য হলাম। মা কত অনুরোধ উপরোধ করলেন। বন্ধুরা কত বোঝাল। আমি নাছোড়। নিয়তির অলঙ্ঘ নির্দেশে আমি যেন মরিয়া। যেন যে কোনো দুঃখ বরণ করতেও আমার বিন্দুমাত্র দ্বিধা নেই।”
সে সময়ের দামাল কিশোর যুবকেরা জাহাজী বা যোদ্ধা হওয়ার নেশায় কতখানি মত্ত ছিল তা শুধু রবিনসন নয়, তার দাদার ক্ষেত্রেও দেখা গিয়েছিল। “বাইরে গেলে অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ – বাবা হয়ে কেমন করে যেতে অনুমতি তিনি দেন। সর্বশেষে আমার বড় ভাইয়ের কথা বললেন। বড় ভাইকেও এই ভাবে বারবার নিষেধ করেছিলেন তিনি, অনিশ্চিতের কোলে ঝাঁপ দিতে মানা করেছিলেন। বড় ভাই শোনে নি তাঁর কথা। জোর করে – একরকম সব কিছু অগ্রাহ্য করেই গিয়ে ভিড়ল সৈন্যদলে। পরিণতি তো মৃত্যু।” এই অমোঘ আকর্ষণ – যার টানে হরেক বিপদের সমূহ সম্ভাবনা, এমনকী যে কোনও সময়ে অতর্কিতে মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে – এসব জেনেও রবিনসন বা তার দাদা বা সেকালের শত সহস্র কিশোর যুবক যোদ্ধা বা জাহাজী হবার জীবন বেছে নিয়েছিল। যুদ্ধে বা সমুদ্রযাত্রায় গিয়ে নিজের ভাগ্য পরিবর্তনের যে গোঁ তারা ধরেছিল পরিবার পরিজনের পরামর্শ বা কাকুতি মিনতির উল্টোদিকে দাঁড়িয়ে – তাকে নির্মাণ করেছিল সেই সময়ের ঔপনিবেশিক ও বাণিজ্যিক অভিযানগুলির নিশিডাক। ড্যানিয়েল ডিফোর রবিনসন ক্রুসোর মত সফল আখ্যান সেই আবহজাত, আবার তার বিপুল সাফল্য শত সহস্র পাঠকের মধ্যে সেই আগ্রহ আকাঙ্ক্ষাকেই আরো উশকে দিয়েছে।
অন্যান্য ইউরোপীয়দের তুলনায় ব্রিটিশরা খানিক দেরিতেই দূর বাণিজ্য ও উপনিবেশ দখলের প্রতিযোগিতায় সামিল হয়েছিল। এর প্রমাণ আছে রবিনসন ক্রুসোর উপলব্ধির মধ্যে। – “বেশির ভাগ নাবিক জানে পর্তুগিজ ভাষা, নয়ত ফরাসি, নয় স্পেন দেশের। ইংরেজি যে বোঝে না কেউ।” পিছিয়ে পড়ার রেশ মিটিয়ে দ্রুত এগিয়ে যাবার যে তাগিদ ব্রিটিশদের মধ্যে সপ্তদশ শতকে দেখা গিয়েছিল, রবিনসন ক্রুশোর জাহাজী হয়ে ওঠা সেই পর্বেরই ব্যাপার।
ঝুঁকি সত্ত্বেও দ্রুত ভাগ্য ফেরাবার সুযোগ হিসেবে জাহাজের কাজে যোগ দেওয়ার জুড়ি ছিল না। রবিনসন জানিয়েছে, “পাকাপাকি নাবিক বনে গেলাম কদিনের মধ্যে। ব্যবসাদারও। ফেরবার সময় খেলনা বেচা লাভের টাকা দিয়ে নিয়ে এলাম পৌনে দু পাউন্ড ওজনের স্বর্ণরেণু। সেটা বিক্রী করে মোট আয় হল তিনশ পাউন্ড। তখন একটা আশা, একটা আত্মবিশ্বাস নিজের মনে জন্ম নিল।” অবশ্য শুধু বড়লোক হবার নেশাই টানে নি রবিনসনদের। দুঃসাহসিক অভিযানে বেড়িয়ে পড়া, দেশ দুনিয়া দেখা ও জয় করার আগ্রহটা নাড়া দিয়েছিল প্রবলভাবে।
অষ্টাদশ শতকে উপন্যাসের বিকাশ প্রতিষ্ঠার প্রেক্ষাপটে থাকা যে সমস্ত বিষয়গুলির কথা ইতিহাসকার ও সমাজ গবেষকরা আমাদের জানিয়েছেন তার একটি হল পাঠক সংখ্যার বৃদ্ধি। ষোড়শ শতকের মাঝামাঝি গুটেনবার্গের ছাপাখানা আবিষ্কার হয় জার্মানীতে এবং কয়েক দশকের মধ্যেই ইউরোপের কোণে কোণে পৌঁছে যায় এই যন্ত্র। সপ্তদশ শতকের মধ্যপর্বে যখন নির্জন দ্বীপে সময় কাটাচ্ছে রবিনসন ক্রুসো সেই সময়টায় ইংলণ্ডে লেখা, পড়া ও ছাপা নিয়ে এক তুমুল আগ্রহের সৃষ্টি হয়েছে। ব্যবসা বাণিজের বিকাশের সঙ্গে নথিপত্র রাখার সরাসরি সম্পর্ক বিদ্যমান। আমরা দেখি নির্জন দ্বীপে চাষবাস, ঘর বানানো, পশুপালন, পরিচ্ছদ তৈরি ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ কাজের পাশাপাশিই রবিনসন ক্রুসো বারবার বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছেন দিনলিপি ও নথিপত্র রাখার ব্যাপারে।
“মানচিত্র এনেছিলাম জাহাজ থেকে, তার হিসেব মিলিয়ে দেখলাম – আমি যে দ্বীপে আছি, সেটা অনামী, ন ডিগ্ৰী বাইশ মিনিট উত্তর অক্ষরেখায় তার অবস্থান। আমি এসেছি এখানে ৩০শে সেপ্টেম্বর। আজ বারো দিন পার হয়ে গেল। এরও একটা হিসেব রাখা দরকার। তখন একটা মস্ত গাছের গায়ে ছুরি দিয়ে খোদাই করে লিখলাম – আমি, এই দ্বীপে ১৬৫৯ সালের ৩০ শে সেপ্টেম্বর এসেছি। তার পাশে বারোটা ক্ষুদে ক্ষুদে দাগ কাটলাম। অর্থাৎ বারো দিন আছি আমি এখানে। দিন যেমন বাড়বে, দাগও একটা একটা করে বাড়বে। মোটমাট এটাই হবে আমার আগামী দিনের দিন-মাস-বছরের ক্যালেন্ডার। খুচরো অনেক কিছুই এনেছি জাহাজ থেকে। তার উল্লেখ আগে করি নি। কেননা সেগুলো মূল্যবান তেমন কিছু নয়, কিন্তু দরকারী বটে আমার কাছে। যেমন কলম, কালি, কাগজ, কাপ্তেনের নামাঙ্কিত কয়েকটা কাগজের মোড়ক, কম্পাস, জ্যামিতিক মাপ কষার কিছু যন্ত্রপাতি, কিছু নকশা, সমুদ্রে জাহাজ চালনা সংক্রান্ত কয়েকখানি বই, একখানা বাইবেল, পর্তুগিজ ভাষায় লেখা খানকতক বই, তার মধ্যে একখানা প্রার্থনাগীতি ধরনের–সব যত্ন করে আমি তুলে রেখেছি আমার অন্যান্য মালপত্রের সঙ্গে।” রবিনসন ক্রুসো শুধু নথি রাখছেন তাই নয়, কালি ফুরিয়ে যাবে ও কীভাবে নথি রাখার ব্যবস্থা করা যাবে, তাই নিয়ে ভীষণ রকম দুশ্চিন্তা শুরু করেছেন। “কলম আছে কালি আছে কাগজ আছে বরং লিখেই ফেলি সবকিছু। তাতে অন্তত নথি বলে একটা জিনিস থাকবে। তখন তাই শুরু করলাম। কিন্তু কালি এক সময় গেল ফুরিয়ে। সে যাকগে, নতুন করে, কীভাবে কালির প্রয়োজন মেটানো যায় সেটা পরের চিন্তা। কিন্তু যে কদিন কালি ছিল দোয়াতে আমি প্রতিটি হিসেব বিবরণী নির্ভুল ভাবে লিখে ফেলেছি খাতায়। যাতে বুঝতে কারো অসুবিধে না হয়। অর্থাৎ কালির প্রয়োজনটা এক্ষেত্রে যত তীব্র, তেমনি প্রয়োজনীয় আমার কাছে কোদাল, কুড়ুল, বেলচা, সুচ, আলপিন, সুতা ইত্যাদি।”… “নিজের অবস্থা নিয়ে আমি কিন্তু বেশ গভীরভাবে ভাবতে শুরু করেছি। লিখেও ফেলেছি আমার বর্তমান অবস্থার বিবরণী। এমন নয় যে এটা কেউ দেখবে সেইজন্যে লেখা। কিংবা আগামী দিনে আমার লেখাটা উদ্ধার পাবে, তখন আমি হয়ত আর বেঁচে থাকব না–সেইজন্যে লেখা। এটা সম্পূর্ণ আমার নিজেরই জন্যে। নিজেকে যাচাই করার প্রশ্নে। নিজেকে নিয়ে ভাববার প্রশ্নে। ভালো কী কী আমার জীবনে সেটা যেমন বুঝবারো প্রয়োজন আছে, মন্দ কী কী এবং কেন সেটাও তেমনি বোঝা দরকার। তা হলে নিজের প্রকৃত অবস্থা আমি বুঝতে পারব কীভাবে।”
আমরা জানি ড্যানিয়েল ডিফো ছিলেন তাঁর সময়ের এক নামজাদা লেখক। শুধু উপন্যাস লিখেই যে তিনি সাড়া জাগিয়েছিলেন তা নয়, বরং আখ্যান লেখার অনেক আগেই জটিল রাজনৈতিক আবর্তের তৎকালীন ব্রিটেনে প্যামফ্লেট লেখক হিসেবে তিনি বিশেষ খ্যাতির অধিকারী হয়েছিলেন। বিভিন্ন রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গের প্রচার নথি লিখে এসেছিল বিপুল অর্থ, যশ ও প্রতিপত্তি। সপ্তদশ অষ্টাদশ শতকে লেখা নথি বই পুস্তিকা ছাপাছাপির ক্ষেত্রে যে আগ্রহের জোয়ার এসেছিল ব্রিটেন ও ইউরোপে, নির্জন দ্বীপে বসবাসকারী রবিনসন ক্রুসোও তার বাইরে থাকতে পারেন নি। এই দিক থেকে বলা যায় যে বুর্জোয়া সমাজ তখন ইংলণ্ডে গড়ে উঠছে, নির্জন দ্বীপবাসী হয়েও রবিনসন ক্রুসো চিন্তা চেতনায় তারই শরিক ছিলেন।
বিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বা একুশ শতকে পোস্ট কলোনিয়াল সাহিত্য সমালোচনার ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ টেক্সট হিসেবে সামনে এসেছে রবিনসন ক্রুসো। সপ্তদশ অষ্টাদশ শতকের ইউরোপীয় ঔপনিবেশিকতার অসংখ্য লক্ষণকে ধারণ করে রয়েছে এই উপন্যাস। দক্ষিণ আমেরিকার বুকে মূলত স্পেনীয় ও পর্তুগীজদের আধিপত্য এবং ব্রিটিশ, জার্মান, ফরাসী, ওলন্দাজ প্রমুখদের আনাগোণা ও ব্যবসা বাণিজ্যের অনেক কথা জানিয়েছে এই উপন্যাসটি। রিয়ালিস্ট ন্যারেটিভের প্রথম দিককার এক উল্লেখযোগ্য প্রতিনিধি হিসেবে ইউরোপীয়দের দাস ব্যবসার অন্তরঙ্গ ছবি তুলে ধরে এই উপন্যাস। লাতিন আমেরিকা ও ক্যারিবীয় অঞ্চলের লক্ষ লক্ষ একর জমিতে তখন আখ চাষের লাভজনক ব্যবসা ফেঁদে বসেছে ইউরোপের ভাগ্যান্বেষীরা। জমির পরিশ্রমসাধ্য কাজের জন্য কাজে লাগানো হচ্ছে আফ্রিকা থেকে ক্রীতদাস হিসেবে বন্দী করে আনা হাজার হাজার কালো মানুষকে। পশুর মতো খাটানো হচ্ছে মাঠ ময়দানে। একদিকে তাদের শ্রম থেকে ফসল তুলছে ইউরোপীয় উদ্যোগপতিরা। অন্যদিকে আবার এই দাস ব্যবসা করে লাখপতি হয়ে যাচ্ছে একদল ইউরোপীয়। দাস ব্যবসার সূত্রে ফুলে ফেঁপে উঠছে ইউরোপের জাহাজ ব্যবসাও। এইরকম এক জাহাজ ব্যবসার সূত্রেই রবিনসন ক্রুসোর প্রথম সাগর পাড়ি দেওয়া।
রবিনসন ক্রুসো উপন্যাসের মধ্যে একটি ঔপনিবেশিক প্রকল্প কীভাবে ধরা আছে, একটি উত্তর ঔপনিবেশিক সমাজের পাঠক হিসেবে সেটা আমরা বিশেষভাবে বুঝতে চাইবো। তবে তার আগে তাকানো যাক প্রাসঙ্গিক ইতিহাসের দিকে। নেওয়া যাক উত্তর ঔপনিবেশিক পাঠের কিছু খোঁজখবর।
ভারতে বাণিজ্য করতে আসার স্বপ্নে মশগুল ক্রিস্টোফার কলম্বাস পঞ্চদশ শতাব্দীর একেবারে শেষভাগে পর্তুগাল থেকে বাণিজ্যতরী নিয়ে বেরিয়ে শেষ পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছন ক্যারিবিয়ান দ্বীপপুঞ্জ ও দক্ষিণ আমেরিকায়। এরপর স্পেন ও পর্তুগালের তরফে বেশ কিছু অভিযান চলে গোটা দক্ষিণ আমেরিকা ও ক্যারিবিয়ান দ্বীপপুঞ্জগুলিতে। ব্রিটিশ, ফরাসী ও অন্যান্য ইউরোপীয় শক্তির লোভী দৃষ্টিও পরে কোনও কোনও অঞ্চলে। মায়া, আজটেক ও ইনকা সভ্যতার অতীতকে প্রায় সম্পূর্ণ মুছে ফেলে লুঠেরা কনকিস্তাদাররা। লক্ষ লক্ষ অধিবাসীকে আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রের সাহায্যে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়। এর ফলে ঔপনিবেশিক শাসন এক নতুন সমস্যার মুখোমুখি হয়। খনি থেকে সোনা রূপো সমেত নানা সম্পদ আহরণ করাই হোক, বা চাষবাস সহ হরেক শ্রমসাধ্য কাজ করাই হোক – তার জন্য লোকের অভাব দেখা যায়। সেই অভাব পূরণ করতে আফ্রিকা থেকে নিয়ে আসা হয় হাজার হাজার মানুষকে। তাদের ক্রীতদাস হিসেবে জুতে দেওয়া হয় নানা কঠোর পরিশ্রমের কাজে, চলে অমানুষিক অত্যাচার। ইউরোপীয় কনকিস্তাদাররা আমেরিকার নিজস্ব সংস্কৃতি, ইতিহাসকে ধ্বংস করে কীভাবে নির্বিচার শোষণ চালিয়েছে সেখানে, কীভাবে শুধু সংস্কৃতি আর ইতিহাস নয়, মানুষগুলিকেই নিকেশ করে দেওয়া হয়েছে, তার বিস্তারিত ও মর্মস্পর্শী ইতিহাস লিখে গেছেন এদুয়ার্দো গালেয়ানো তাঁর “লাতিন আমেরিকার রক্তাক্ত ইতিহাস” বইতে। লাতিন আমেরিকা জুড়ে একদিকে আদিবাসীদের নিকেশ করা হল, অন্যদিকে চাষবাস আর খনিতে কাজের মজুর নিয়োগের জন্য দাস হিসেবে আমেরিকায় নিয়ে আসা শুরু হল হাজার হাজার আফ্রিকী কালো মানুষকে৷ পরে আফ্রিকার দেশগুলোকে সরাসরি উপনিবেশও বানিয়েছিল ইউরোপীয় শক্তিগুলো।
রবীন্দ্রনাথ তাঁর ‘আফ্রিকা’ কবিতায় ভারতের নিজস্ব ঔপনিবেশিক যন্ত্রণা থেকে আফ্রিকার মানুষের সমস্যাকে বুঝতে চেয়েছিলেন। বিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে যখন প্রত্যক্ষ ঔপনিবেশিক শাসন থেকে দেশগুলো একে একে মুক্তি পাচ্ছে, তখন সর্বত্রই উঠে আসতে দেখা গেল দেখা গেল উত্তর ঔপনিবেশিক সাহিত্যের নতুন চিন্তা চেতনা। সেখানে একদিকে যেমন উপনিবেশের শাসন শোষণ ও সংস্কৃতি নির্মাণের কথা এল, তেমনি এল ডি কলোনিয়ালিটির প্রসঙ্গ, প্রাক ঔপনিবেশিক সংস্কৃতিকে আঁকড়ে ধরার আকুতি। একদিকে লাতিন আমেরিকার লেখকেরা, অন্যদিকে আফ্রিকার কবি ঔপন্যাসিক নাট্যকাররা উপনিবেশের রক্তাক্ত বাস্তবের বিনির্মাণ প্রয়াসী হলেন। এই কাজ করতে গিয়ে তাঁরা একদিকে যেমন ইউরোপের জ্ঞানতাত্ত্বিক নির্মাণের মধ্যে লুকিয়ে থাকা ঔপনিবেশিক প্রকল্পগুলিকে মেলে ধরলেন, তেমনি অন্যদিকে প্রাক ঔপনিবেশিক সংস্কৃতি ইতিহাসের হারিয়ে যাওয়া শিকড় খুঁজতে বেরোলেন। গার্সিয়া মার্কেজ তাঁর নোবেল বক্তৃতাতেই তুললেন লাতিন আমেরিকার নিঃসঙ্গতার কথা। লাতিন আমেরিকার মিথ তাঁর লেখায় ঘুরে ফিরে এল। লাতিন আমেরিকার বাস্তবতা যে ইউরোপীয় বাস্তবতা থেকে আলাদা, তাকে প্রকাশ করার জন্য ভাবতে হল জাদু বাস্তবতা নামে এক নতুন শৈলির কথা। গুয়েতেমালার নোবেল জয়ী ঔপন্যাসিক আস্তুরিয়াস মায়া কিংবদন্তী ও উপকথা সংগ্রহ করেছেন, আফ্রিকী ও ইউরোপীয় সংস্করদের যে নামে ডাকা হয়, সেই মুলাটো নামে লিখেছেন চমকপ্রদ এক আখ্যান, যেখানে তিনটি পরতে রয়েছে মায়া, কনকিস্তাদোর আর আফ্রিকা থেকে উপড়ে আনা ক্রীতদাসদের ভাবনার তিনটি ধারা। মেক্সিকোর কথাকার হুয়ান রুলফো হালিস্কোর গল্পগুলোয় বলেছেন রেড ইন্ডিয়ানদের বিপদের কথা, ব্রাজিলের পাওলো ফ্রেরীর লেখাতেও সেই মুক সংস্কৃতির কথা উঠে এসেছে। মেক্সিকোর আরেক লেখক কার্লোস ফুয়েন্তেস তাঁর একাধিক উপন্যাসে অতীতে ডুব দিয়ে পুরনো সংস্কৃতি ইতিহাসকে খুঁজতে চেয়েছেন। গোটা স্প্যানিশ আমেরিকা বা পর্তুগীজ শাসিত ব্রাজিলের মতো একই অবস্থা ছিল ক্যারিবিয়ান দ্বীপপুঞ্জের ফরাসী উপনিবেশ হাইতিতেও। ফরাসী বিপ্লবের প্রেক্ষাপটে সেখানেই নয়া দুনিয়ার প্রথম দাস বিদ্রোহ ঘটে এবং সেই বিদ্রোহের সূত্র ধরেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পর দ্বিতীয় দেশ হিসেবে উপনিবেশবাদের জোয়াল ছিঁড়ে স্বাধীন দেশ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে হাইতি। কিউবার লেখক আলেহো কার্পেন্তিয়ের হাইতির সেই দাস বিদ্রোহকে অবলম্বন করেই লেখেন তাঁর বিখ্যাত উপন্যাস ‘এই মর্তের রাজত্ব’। কার্পেন্তিয়ের ছিলেন লাতিন আমেরিকান মাটিতে আফ্রিকান ক্রীতদাসদের সূত্রে আসা আফ্রিকি সংযোগসমূহ আবিষ্কারের একজন উৎসাহী গবেষক ও লেখক। সঙ্গীতশাস্ত্রের একজন বিশিষ্ট পণ্ডিত হিসেবে তিনি কিউবার সঙ্গীতে আফ্রিকান উপাদানসমূহ বিষয়ে অসামান্য গবেষণা করেছেন। আফ্রিকার দিকপাল সাহিত্যিকরা, যেমন তায়েব সালিহ, চিনুয়া আচিবি, ওলে সোয়েঙ্কা, এনগুগি ওয়া থিয়ং, এমে সেজেয়ার তাঁদের আখ্যান, নাটক, কবিতায় উত্তর ঔপনিবেশিক স্বরটিকে সন্ধান করেছেন নিজ নিজ দেশীয় প্রেক্ষাপট ও ইতিহাস, সংস্কৃতির আধারে।
রবিনসন ক্রুসো উপনিবেশের সংস্কৃতি কীভাবে নির্মাণ করে সেই আলোচনায় যাবার আগে আরেকটি দুনিয়া বিখ্যাত বই এর দিকে তাকানো যাক। সেটি হল শেক্সপীয়রের ‘টেম্পেস্ট’। কলম্বাসের আমেরিকা আবিষ্কার ও ইউরোপীয় অভিযানগুলির মাধ্যমে লুটপাট চলার সময়েই এই নাটক লিখেছিলেন শেক্সপীয়র। সেখানে ইউরোপীয় নায়ক প্রস্পেরো দাস বানায় ক্যালিবানকে, যে শব্দটিকে বর্বর ক্যানিবাল শব্দের ইচ্ছাকৃত বিপর্যাস ঘটিয়ে তৈরি করা হয়েছে বলেই মনে করেন অনেকে। প্রস্পেরো শুধু ক্যালিবানের শরীর আর কাজের ওপরই প্রভুত্ব স্থাপণ করে নি। তাকে শিখিয়েছে নিজের ভাষা আর এর মাধ্যমে তার চিন্তা চেতনা ও যাবতীয় প্রকাশভঙ্গীর ওপরও নিজের নিয়ন্ত্রণ কায়েম করেছে।
আসা যাক রবিনসন ক্রুসোর প্রসঙ্গে। দেখা যাক তা কীভাবে নিজের শব্দশরীরে সে ধারণ করে আছে ঔপনিবেশিকতাকে।
নাবিক রবিনসন কীভাবে জলদস্যুদের হাতে বন্দী হলেন ও বুদ্ধি খাটিয়ে কিছুদিন পর পালালেন, সে সব রোমহর্ষক বর্ণনা উপন্যাসের আকর্ষণ বৃদ্ধি করেছে। তবে সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক ইতিহাসের দিক থেকে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ উদ্ধারকারী জাহাজ মালিকের পরামর্শে তার ব্রাজিলে আসা ও সেখানে ব্যবসায়িক উদ্যোগ স্থাপণ। আখ্যানে রবিনসন ক্রুসো জানিয়েছে – “সজ্জন এক ব্যক্তির সাথে পরিচিত হলাম। অমায়িক এবং এক কথায় ভদ্রলোক বলতে যা বোঝায়। ছোটো ব্যবসা। একই সাথে আখের চাষ আর আখ থেকে চিনি তৈরির কারবার। আমাকে প্রথম দিকে তার বাড়িতেই ঠাই দিলেন। শিখলাম সব। কেমন করে চাষ করতে হয়, কেমন করে চিনি তৈরি করে, কী তার কৌশল–সমস্ত কিছু। ব্যবসা হিসেবে চমৎকার। খুব ছোটো থেকে আরম্ভ করে অনেকেই এখন বিরাট ধনী হয়ে গেছে। ঠিক করলাম, আমিও এই ব্যবসা শুরু করব। তখন সব ব্যবস্থা তিনি করে দিলেন। এমনকি জমি কেনা থেকে কল কিনে দেওয়া অব্দি। টাকা আমিই দিলাম।”
ব্যবসা একটু বাড়তেই রবিনসন ক্রুসো একে আরো গতি দেবারো জন্য ক্রীতদাস আনার কথা ভাবতে শুরু করেন। অন্যান্য ইউরোপীয়, যারা ব্রাজিলের ঐ অঞ্চলে একই ধরনের ব্যবসা ফেঁদেছিলেন, তাদের মনোভাবও ছিল একই ধরনের। তা্রা ভাবতে শুরু করেন দাস নিয়ে আসার প্রক্রিয়া পদ্ধতি সম্পর্কে। একটা সিদ্ধান্তেও তারা পৌঁছন। – “ব্রাজিলে কাটল আমার টানা চার বছর। মোটের উপর ভালোই চলছে আমার চাষের কাজ। ভাষাটা এতদিনে বেশ রপ্ত হয়েছে। বন্ধুত্ব হয়েছে বিস্তর মানুষের সঙ্গে। তার মধ্যে কিছু কিছু ব্যবসায়ী বন্ধুও আছে। তারা মূলত সালভাদোরের বাসিন্দা। বন্দর তো। মাল চালান দেবার প্রয়োজনে আমাকে প্রায় তাই যাতায়ত করতে হয়। খোসগল্পের আসর বসে। বলি আমার সমুদ্রযাত্রার কাহিনী। সুলভে স্বর্ণরেণু আনার গল্পও বলি। তাছাড়া আরো যে সব ব্যবসা চলে গিনিতে ছুরি কাচি খেলনা পুঁতি কুড়ল – তারও বিবরণ দিই। বিনিময়ে মেলে গজদন্ত প্রভৃতি নানান মূল্যবান সামগ্রী। তাছাড়া নিগ্রোও ধরে আনা যায়। ব্যবসা হিসেবে সেটাও কিছু মন্দ নয়।
খুবই মন দিয়ে শোনে আমার কথা। আগ্রহ দেখি প্রচণ্ড। তবে নিগ্রো আনার ব্যাপারটা সম্বন্ধে একটু আপত্তি করে। এখনো রাজার স্বীকৃতি মেলে নি এ ব্যাপারে। স্পেন বা পর্তুগালে এখনো এ ব্যবসা রমরমা নয়। তবু নিয়ে আসে কেউ কেউ নিজের প্রয়োজনে। অথবা বিক্রী করলেও তাকে প্রয়োজন বলে দেখায়। মোটমাট এভাবেই চোরাগোপ্তা পথে মানুষ বিক্রীর ব্যবসা চলে।
একদিন সকালে দেখি তিন ব্যবসাদার আমার বাড়িতে এসে হাজির। মাত্র তার আগের দিনই এক ভোজের আসরে তিনজনকে শুনিয়েছি আমার সমুদ্রযাত্রার বিবরণ। নিগ্রো প্রসঙ্গও সেখানে স্বাভাবিক নিয়মে এসেছে। তো বলে, আপনার সঙ্গে গোপন কথা আছে। বললাম, কী কথা? বলল, ঐ ব্যবসা প্রসঙ্গেই আমাদের একটা প্রস্তাব আছে। সারারাত ধরে ভেবেছি আমরা তিনজন। এই যে এত বড় বড় ক্ষেত আমাদের, তাতে পারি না একা হাতে চাষবাস করতে। পড়ে থাকে অঢেল জমি। অনেকটা আপনারই মতো। এ অবস্থায় যদি কাজের প্রয়োজনে কিছু নিগ্রো আমরা নিয়ে আসি গিনি থেকে? আপনার কী মত? ভালো জাহাজ নিয়ে বেরিয়ে পড়ব। আপনিও আমাদের সঙ্গে থাকবেন। কেনাকাটার যাবতীয় দায়িত্ব আপনার। না না, টাকা আপনার লাগবে না, সব আমাদের। শুধু বুদ্ধি আপনার। আর কাজ হাসিল। বিনিময়ে আপনিও কিছু নিগ্রো পাবেন। এটা আপনার দস্তুরী।”
প্রস্তাবটি লোভনীয় মনে হয় রবিনসন ক্রুসোর। তিনি পরিকল্পনা অনুযায়ী বেড়িয়ে পড়েন। এই অভিযানে বেরিয়েই তার জাহাজডুবি হয় এবং তিনি ভাসতে ভাসতে কোনওক্রমে প্রাণ নিয়ে পৌঁছতে পারেন জনমানবহীন এক নির্জন দ্বীপে, যেখানে পরবর্তী আড়াই দশক তিনি থাকবেন একাকী।
শেষমেষ একজন সঙ্গীকে পান রবিনসন ক্রুসো। হত্যাকারীদের হাত থেকে গুলি ছুঁড়ে বাঁচানোর পর সে ক্রুসোর অনুগত দাস হিসেবে থাকতে শুরু করে সেই দ্বীপে। ক্রুসো তার নামকরণ করেন আর শেখান ভাষা। সেই প্রস্পেরো যেভাবে ক্যালিবানকে ভাষা শিখিয়েছিলেন। “প্রথম কাজ আমার তাকে কথা শেখানো অর্থাৎ আমার ভাষা। নইলে তো কেউ বুঝবে না কারা মনের ভাব। তারও আগে দরকার ওর একটা নাম। কিন্তু কী নাম দিই। তখন মনে এল বারটার কথা। আজ তো শুক্রবার। ইংরিজিতে বলে ফ্রাইডে। হোক না ওর নাম তাই। অর্থাৎ ফ্রাইডে। সেটা বুঝিয়ে দিলাম। দেখি ভারি খুশি। হ্যাঁ আর না বলতে শেখালাম। শিখে নিল চটপট।” … “ভাষা বোঝে না আমার। আমিও বুঝতে পারি না ওর ভাষা। কীভাবে বোঝাব ওকে সব কিছু? তখন ঠিক করলাম, আর কিছু শেখাবার আগে ওকে ভাষাটা শেখাতে হবে। শুরু হল তারই প্রচেষ্টা।”
মালিকের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা এক ‘আদর্শ দাস’ চরিত্র হিসেবে রবিনসন ক্রুসোর আখ্যানে ফ্রাইডেকে সামনে আনা হয়েছে, যে শুধু প্রভুর কাজ করে না, তাকে শ্রদ্ধা আর ভালোবাসাতেও ভরিয়ে দেয়। “ফ্রাইডেকে নিয়ে কাজে লেগে পড়লাম। অদ্ভুত ক্ষমতা ওর। খাটতে পারে প্রচণ্ড। আমাকে বলল, মালিক, আপনাকে এতো খাটতে হবে না। আমি তো আছি। বলে দিন আমাকে কী কী করতে হবে। সব আমি করব। আপনি শুধু বসে বসে দেখুন।
আমার যেন হাতে স্বর্গ পাওয়ার অবস্থা। এর চেয়ে সুখ আর কী থাকতে পারে জীবনে! ছিলাম পঁচিশটা বছর একাকী, সঙ্গী পেলাম তার পরে। মনের মতো সঙ্গী। এতদিন জানত না নিজের মনের ভাব ব্যক্ত করতে। অর্থাৎ আমাকে বোঝাতে পারত না। ইদানীং তা-ও পারে। শিখে নিয়েছে অনেক নতুন নতুন কথা। সেটা আমার কাছে বিরাট একটা ব্যাপার। আমিও জবাবে কিছু বলতে পারি। এতদিনকার বোবা জিভে আবার ভাষা ফুটতে শুরু করেছে। ভারি তৃপ্তি পাই ওর সাথে কথা বলে। এত সরল এত অকপট ওর মন। আর ভীষণ শ্রদ্ধা করে আমাকে। প্রাণ দিয়ে ভালবাসে।”
কিন্তু শুধু কাজ, বিশ্বাস আর ভালোবাসাই শেষ কথা নয়। প্রভুর চাই দাসের মন ও বিশ্বাসের ওপর সম্পূর্ণ অধিকার। যাতে বিদ্রোহ বিস্ফোরণের সম্ভাবনাকে দূর করা যায়। এজন্য দরকার ধর্মের। শাসক প্রভুর ধর্মে শাসিত দাসকে নিয়ে আসার। ইউরোপীয়রা যেখানে যেখানে উপনিবেশ গড়েছে, ব্যবসার নিয়ন্ত্রণ নিয়েছে, সেখানে সেখানেই তারা নিজেদের ধর্মকে ছড়িয়ে দেবার চেষ্টা করেছে। লাতিন আমেরিকা জুড়ে কনকিস্তাদাররা যখন একহাতে আদিবাসীদের থেকে জমির দলিল নিয়েছে, তখন অন্য হাতে তারা আদিবাসীদের তুলে দিয়েছে বাইবেল। ফ্রাইডেকে নিজের ধর্মে ও বিশ্বাসে কীভাবে আনতে চেয়েছেন রবিনসন ক্রুসো, উপন্যাসে তার একটা বিস্তারিত বর্ণনা আছে। সেটা খেয়াল করা যাক।
“এই যে এতদিন ফ্রাইডে আছে আমার সঙ্গে – ছায়ার মতো পাশে পাশে ঘোরে, খায় একসাথে বসে, ঘুমোয় – একবারও কিন্তু ওর মনে ধর্মীয় চিন্তা জাগিয়ে তোলার এতটুকু চেষ্টা আমি করি নি। একদিন কথায় কথায় জিজ্ঞেস করেছিলাম, কে তার স্রষ্টা। কথাটার মানে সে একদম বুঝতে পারে নি, হাঁ করে তাকিয়ে রইল আমার মুখের দিকে। তখন বললাম, আচ্ছা বলত দেখি, এই সাগর কার হাতে তৈরি, কিংবা এই পায়ের নিচের মাটি বা মাথার ওপরের আকাশ? বলল, কে আমার বনামুকি। সে থাকে ওই হোথায় – বলে দূরে আকাশটা দেখিয়ে দিল। বললাম, সে অবার কে? বলল, জানো না তুমি? সে মস্ত বড় মানুষ। তার অঢেল ক্ষমতা। আর অনেক বয়েস। এই সাগর মাটি পাহাড় চাঁদ সূর্যের চেয়েও বয়েসে অনেক বড়ো। বুড়ো থুথুড়ে। বললাম, বেশ তো, নয় মানলাম তোর কথা, ধরে নিলাম তোর বেনামুকিই সৃষ্টি করেছে সব। তবে সকলে বেনামুকিকে পুজো করে না কেন? কী গম্ভীর তখন ফ্রাইডের মুখ! যেন বিরাট এক কূট তর্কের সুচিন্তিত মতামত দিতে চলেছে, সেই রকমই ভাব। বলল, করে তো। সবাই পুজো করে। পুজো করে বলেই তো আকাশ গোল, সাগর গোল, মাটি গোল, পাথর গোল – সব গোল। পুজো মানেই গোল। বললাম, আর যারা মারা যায় তারা? কোথা যায় মৃত্যুর পর? বলল, বেনামুক্তির কাছে। কী করে তখন বেনামুকি? সবাইকে পটাপট গিলে খায়? বলল, হ্যাঁ, খুব খিদে তার। তাই খায়।
তারপর থেকেই তার মনে ঈশ্বর সম্পর্কে প্রকৃত বোধ জাগিয়ে তোলার প্রচেষ্টা শুরু করি। বললাম, সত্যিকারের ঈশ্বর কোথায় থাকেন জানিস, ঐ আকাশে। ওর ওধারে স্বর্গ। তারই কর্তৃত্বে চলে এই গ্রহ নক্ষত্র তারা। চলে এই পৃথিবী। তিনি স্বয়ং সম্পূর্ণ অর্থাৎ একাই অসীম শক্তির অধিকারী। কারুর সাহায্য তার দরকার লাগে না। আমাদের সব যেমন তিনি দুহাত ভরে ঢেলে দেন, আবার ইচ্ছে হলে সব কিছু কেড়েও নেন তিনিই।
দেখি শুনছে খুব মন দিয়ে। সারা চোখে মুখে অদ্ভুত আগ্রহের দ্যুতি।
তখন যীশু খ্রিস্টের গল্প বললাম। তার সৃষ্ট প্রার্থনার কথা বললাম। ঈশ্বর স্বয়ং পাঠিয়েছেন তাঁকে এই পৃথিবীতে তাই তো আশ্চর্য শক্তি নিয়ে রচনা করতে পেরেছেন অনবদ্য সব প্রার্থনা গীতি। সে প্রার্থনা ঈশ্বর স্বর্গ থেকেও শুনতে পান।
ফ্রাইডে বলল, তবে তো বেনামুকির চেয়ে তিনি অনেক অ-নে-ক বড়। সে তো থাকে ঐ পাহাড়ের মাথায়। তবু কই সব কথা যে শুনতে পায় না।
বললাম, তুই বুঝি পাহাড়ের মাথায় বেনামুকির সঙ্গে কথা বলতে গিয়েছিলি?
বলল, না না, আমরা যাই নি। আমাদের যাবার নিয়ম নেই। কম বয়েস যে আমাদের। যায় বুড়োর দল। তারা উকাকী। তারা বেনামুকির সঙ্গে কীভাবে কথা বলতে হয় জানে।
উকাকী অর্থাৎ ধর্মীয় সম্প্রদায়ের লোকজন। এটা আমি প্রশ্ন করে জেনে নিলাম।
বললাম, তারপর?
– তারপর আর কী? সব জেনে ফিরে আসে তারা। বেনামুকী কী বলল আমাদের এসে বলে। আমরা সেই ভাবেই কাজ করি।
অর্থাৎ ধর্মের নামে বুজরুকি। সভ্য জগতের সঙ্গে নেই কিছুমাত্র সংযোগ বা সংস্পর্শ, ধর্মের নামে এখানেও চলে নানান কলা কৌশল। পৃথিবীর সব দেশেই হয়ত এটাই চিরাচরিত প্রথা।
তবে ভুল ভাঙানোটা দরকার। দরকার মন থেকে এই অন্ধ বিশ্বাস দূর করা। বললাম – দেখরে, এই যে বুড়ো মানুষদের পাহাড়ের মাথায় গিয়ে বেনামুকির সাথে কথা বলে সব জেনে ফিরে আসা গোটা ব্যাপারটাই মিথ্যে, ভুয়ো। এর মধ্যে সত্যের নামগন্ধ নেই। তোদের এইভাবে ওরা দিনের পর দিন ঠকায়। যদি সত্যি সত্যি সেই নির্জনে কারুর সঙ্গে তারা কথা বলে তবে সে ঈশ্বর নয়, পিশাচ। পিশাচই বাস করে একমাত্র ঐ নির্জন বন্ধুর পরিবেশে।
বলে পিশাচ কী, কেমন ভাবে তার জন্ম হয়। বাইবেলে এ সম্বন্ধে কী লেখা আছে – সব বললাম। শুনল মন দিয়ে। তবু ঐ – চট করে কি আর বিশ্বাস যায়! মনে যে এতদিনের ক্লেদ গ্লানি আর কুসংস্কারের বীজ। তখন শুরু করলাম একদম গোড়া থেকে। এই বিশ্ব, তার জন্ম, তার সৃষ্টিতে ঈশ্বরের অবদান, আমাদের জন্ম, আমাদের প্রতিটি ক্রিয়াকলাপ, আমাদের পুণ্য, আমাদের পাপ – সব একটু একটু করে ব্যাখ্যা করে, উদাহরণ দিয়ে বোঝালাম। দেখি শুনছে ভারি তন্ময় হয়ে। আর চোখে বিশ্বাসের ঝিলিক।”
উপনিবেশ কীভাবে প্রভু আর দাসের জগৎ তৈরি করে তা শুধু শোষণ, লুন্ঠন আর অত্যাচারের কাহিনী দিয়ে বোঝা যাবে না। বোঝা যাবে না কেবলমাত্র বাজার, অর্থনীতি, লাভ ক্ষতির হিসেবটুকু দিয়েও। সামগ্রিক ভাবে ঔপনিবেশিকতাকে বুঝতে হলে জানতে হবে উপনিবেশের মাটিতে ও মননে শাসিতের ধর্ম, ইতিহাস, সভ্যতা সংস্কৃতির ওপর নিরন্তর হামলা ও অন্তর্ঘাতের ইতিবৃত্তকে। বুঝতে হবে জ্ঞান ও শিক্ষার জগতকে উথালপাতাল করে কালো বা বাদামি চামড়ার মানুষদের মন আর চোখকে সাদাদের পৃথিবীর মতো করে তোলার প্রকল্পকে। সেটা ভারত বা এশিয়ার বিভিন্ন দেশের জন্য যেমন সত্য, তেমনই সত্য লাতিন আমেরিকা, ক্যারিবীয় অঞ্চল বা আফ্রিকার জন্য – গোটা ঔপনিবেশিক দুনিয়ার জন্য।