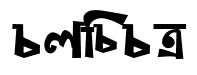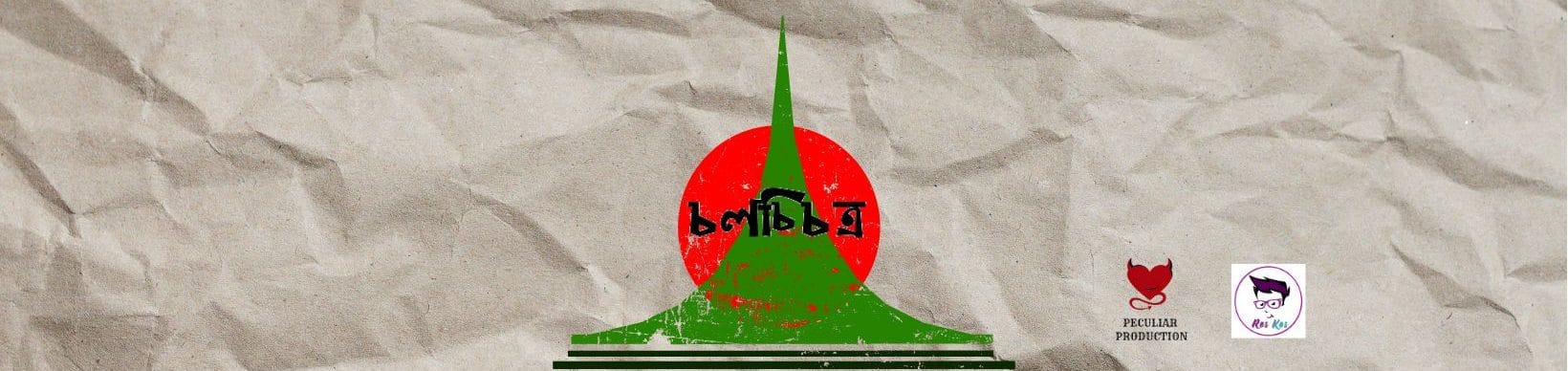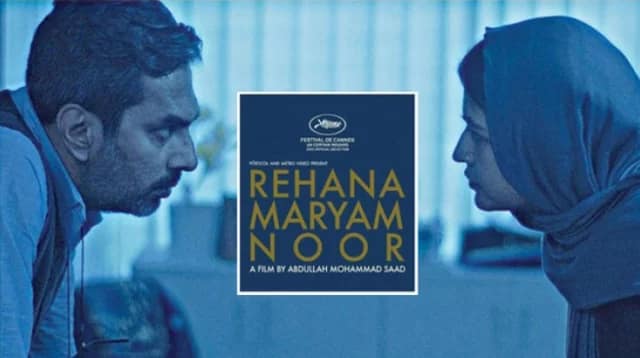কোনো সিনেমা দেখার আগেই তার গল্প ও পজেটিভ-নিগেটিভ সমালোচনা পড়ে ফেলা, শুনে ফেলা, জেনে ফেলা নিঃসন্দেহে ছবি দেখার আনন্দ কমিয়ে দেয়। কিন্তু রেহানা মরিয়ম নূরের ক্ষেত্রে এর কোনোটাই এড়ানো গেলো না। সেটা স্বাভাবিকও। এই প্রথম বাংলাদেশের কোনো ছবি আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র অঙ্গনে এতো দূর গিয়েছে। এই অর্জন সামান্য নয়।

ছবিটা দেখার সময় বারবারই এই পরিচালকের প্রথম ছবি ‘লাইভ ফ্রম ঢাকা’র কথা মনে পড়ছিলো। মনে পড়ছিলো এজন্য নয় যে, তিনি একই সব বিষয়-আশয় রিপিটেশন করেছেন। বরং এজন্য যে, অসামান্য প্রতিভাধর এই নির্মাতা তার কাজের নিজস্ব স্টাইল বজায় রেখেছেন। শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত ফ্রেম ধরা, এক দৃশ্য থেকে অন্য দৃশ্যে চলাচল এবং ছবির ক্লোজার- পুরোটাতেই নির্মাতার সিগনেচার আছে। শক্তিশালী পরিচালক ছাড়া এমনটা সম্ভব নয়।
দেখার আগেই শুনেছিলাম, গল্পটা বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে ‘মি-টু’ আন্দোলনের পটভূমিতে বাংলাদেশের গল্প নিয়ে করা। আমি ব্যক্তিগতভাবে নারীবাদী বিষয়-আশয় নিয়ে পুরুষ পরিচালকের তৈরি করা সিনেমাগুলোকে সন্দেহ করি। সেই সন্দেহ থেকে ছাত্রজীবনে এ ধরনের কিছু ছবি নিয়ে মাস্টার্স থিসিসও করেছিলাম। গবেষণার ফলাফলও আমার পূর্বানুমানের পক্ষেই গিয়েছিলো। পুরুষ পরিচালকেরা নারীর গল্প বলতে পারেন না বা নারীর গল্প বলে তারা যা সব তৈরি করেন, নারী দর্শকরা সেসবকে নারীর গল্প বলে সব সময় স্বীকারও করেন না। এখানে বলে রাখা ভালো, আমার গবেষণার নমুনা ছবিগুলো ছিলো যথাক্রমে- নাসির উদ্দিন ইউসুফ বাচ্চুর ‘গেরিলা’, মোস্তফা সারোয়ার ফারুকীর ‘থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার’ এবং তানিম নূরের ‘ফিরে এসো বেহুলা’।
রেহানা মারিয়াম নূর আমার ভালো লাগবে না, ম্যানসপ্লেইনিং এর দোষে দুষ্ট বলে মনে হবে। এই আশঙ্কা মনে নিয়েই আমি সিনেমাটা দেখতে গিয়েছিলাম। দেখার পর অনেকেই জানতে চেয়েছেন, কেমন লাগলো। কেউ কেউ রিভিউ লিখতে বলেছেন। কেমন লাগলো প্রশ্নের জবাবে, এক কথায় ভালো বা খারাপ বলার কোনো সুযোগ নেই। ফলে, লেখাই শ্রেয় মনে করলাম। সমালোচনা করতে গিয়ে খারিজ করে দেওয়া বা প্রশংসা করতে গিয়ে আকাশে তুলে ফেলার পক্ষপাতী আমি নই। মানুষ মাত্রই নানা রকমভাবে বায়াসড্ হয়, আমি আমার বায়াসনেসগুলোর কথা আগেই বলেছি। বলা বাহুল্য আমার বায়াসনেস এ ক্ষেত্রে দ্বিমুখী। নির্মাতার প্রথম ছবি দেখার মুগ্ধতা, বর্তমান ছবিটির অভূতপূর্ব সাফল্য একদিকে, অন্যদিকে আমার নিজস্ব নারীবাদী দৃষ্টিভঙ্গি এবং এইরকমের এজেন্ডা ছবি, বিশেষত নারীবাদী এজেন্ডা ছবি সম্পর্কে এক ধরনের বিমুখতা। পরস্পর বিরোধী এই দুই মানসিক দশা নিয়েই ছবিটি দেখেছি এবং আলোচনা করারও সাহস করছি।

ছবির রিভিউ লিখতে গিয়ে গল্পটা বলে ফেলা অত্যন্ত বিরক্তিকর। এই ছবির ক্ষেত্রে যদিও স্পয়লার হয়ে যাওয়ার তেমন কোনো চান্স নেই। ছবির গল্প সবারই জানা, ইতিবাচক ও নেতিবাচক দিকগুলোও কম বেশি সবাই শুনে ফেলেছেন। তাই গল্প বলার ঝামেলায় না গিয়ে এবং স্পয়লার হয়ে যাওয়ার ভয় না পেয়ে, ছবিটার সবচেয়ে সবল দিকগুলো ও সবচেয়ে দুর্বল দিকটি নিয়ে কথা বলতে চাচ্ছি।
আগেই বলেছি, না চাইলেও ছবির আগাপাশতলা জেনে ফেলেছিলাম। শুনলাম, পুরো ছবিটাই ভালো। কিন্তু শেষে গিয়ে রেহানা তার সন্তানের সঙ্গে যে নিষ্ঠুর আচরণ করেন- তা অনেকের কাছেই গ্রহণযোগ্য মনে হয়নি। আমার মতে সিনেমার ক্লোজারে রেহানা তার মেয়ে ইমুকে ঘরে আটকে ফেলার পর ইমু যে চিৎকার করে কাঁদতে থাকে- সেই কান্না ও চিৎকার এই ছবির সবচেয়ে শক্তিশালী সিনেমাটিক ল্যাঙ্গুয়েজের ব্যবহার। কোনো রকমভাবে ভিকটিম কার্ড না খেলেও অসহায়ত্বের প্রকাশ ঘটানো এই দৃশ্যটি একদম বাজিমাত করে দিয়েছে। শেষ দৃশ্যটিই এই সিনেমার মেসেজকে স্পষ্ট করে। নারীর জীবনের আটকদশার এমন প্রতীকী প্রকাশ একেবারে এক দাগে যা বলার বলে দিয়েছে। এই ছবিটা এইভাবে এবং এইভাবেই শেষ হতে পারতো।
নারীবাদী সাহিত্যের ইতিহাসে নরওয়েজিয়ান লেখক হেনরিক ইবসেনের নাটক ‘আ ডলস হাউজ’ একটা মাইলফলক। ডলস হাউজের শেষ দৃশ্যে নোরা তার সংসার সন্তান ছেড়ে চলে যাওয়ার সময় পেছনে সশব্দে দরজাটা স্ল্যাম করে যায়। বলা হয়, নোরার সেই দরজার শব্দ পরবর্তী এক শ বছর নারীর আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার প্রশ্নের সঙ্গে প্রতিধ্বনিত হয়েছে। ইবসেনের নোরার দরজা খুলে বের হয়ে যাওয়ার সঙ্গে সাদের রেহানার কন্যাকে ঘরের ভেতর রেখে দরজা আটকে দেওয়ার একটা অদ্ভুত মিল আছে। এই সময়ে এসে আপাতদৃষ্টিতে নারীর জীবনে আর্থিক সঙ্গতি এসেছে, এসেছে কর্মময় জীবন। অথচ ন্যায়বিচারের প্রশ্নে রেহানাকে যেমন করে আপোষ করতে হলো, যেভাবে আটকে ফেলা হলো, তাকে বিচারের দাবি প্রত্যাহার করতে হলো, সেই দমবন্ধ, নিরুপায় ভবিষ্যৎ দেখা যায় এই শেষ দৃশ্যে।
গল্পের মধ্যেও রেহানা এবং তার কন্যাসন্তানের জীবনের ক্রাইসিস প্যারালালি চলতে থাকে। দিনের পর দিন সহপাঠীর অ্যাবিউসিভ বিহেভিয়ার সহ্য করতে করতে বাচ্চা মেয়েটি যখন ভায়োলেন্ট হয়ে ওঠে, সবার আঙ্গুল ওঠে তার দিকেই। ইমুর মতো তার মা রেহানা এবং আমাদের মতো হাজার হাজার নারীর জীবনেও কি একই বাস্তবতা নয়? রাস্তাঘাটে যৌন নিপীড়নের বিরুদ্ধে আওয়াজ তোলা মেয়েটাকেই কি সব সময় বলা হয় না, ‘চুপ করো, চুপ থাকো, থামো, ভদ্রঘরের মেয়েরা এভাবে কথা বলে না, শিক্ষিত পরিবারের মেয়েরা গালাগাল করে না’? আমরা সবাই কি এই অভিজ্ঞতার ভেতর দিয়ে কম বেশি যাইনি?
ক্যারেক্টার কন্সট্রাকশন আর অভিনেতাদের অভিনয় সম্পর্কে না বললেই নয়। নাম ভূমিকায় বাঁধনের অভিনয় তো আছেই, ইমু চরিত্রে আফিয়া জাহিন এবং অ্যানি চরিত্রে আফিয়া তাবাসসুম রীতিমতো ফ্যাসিনেটিং অভিনয় করেছেন। তাদের কথা আলাদাভাবে উল্লেখ করলাম এইজন্য যে, এই চরিত্রগুলো বিভিন্ন রকম ইমোশনাল দশার মধ্য দিয়ে যায়- অভিনেতাদের একজন অল্প বয়সের আরেকজন তো রীতিমতো মাত্র ডিম ফুটে বের হওয়া পক্ষীশাবকের মতো ছোট্ট!
রেহানার ইসলামিক আউটফিট এবং বিশ্বাসী যাপন পদ্ধতির বিপরীতে প্রিন্সিপালকে নারী ও সনাতন ধর্মের দেখিয়ে একধরনের ব্যালান্স আনার চেষ্টা করা হয়েছে সম্ভবতো। যে কোনো পলিটিক্যাল সিনেমায় এই রকমের ব্যালান্সিংয়ের দরকার পড়ে। হলিউড ছবিতে সাদা-কালো মানুষের চরিত্র নির্মাণে কাস্টিংয়ে এরকম ব্যালান্সিং করার চর্চা আমরা হামেশাই দেখে থাকি।
দুনিয়ার সিনেমার ইতিহাসে উইমেন্স ফিল্ম বা নারী প্রটাগনিস্ট নিয়ে তৈরি নারীকেন্দ্রিক চলচ্চিত্রের অভাব নেই। রাশিয়ান ছবি ‘টু উইমেন’ থেকে হলিউডের ‘সল্ট’ পর্যন্ত এবং বাংলাদেশের সিনেমায় ‘বেদের মেয়ে জ্যোৎস্না’, ‘গোলাপি এখন ট্রেনে’ থেকে ‘রানী কেন ডাকাত’ পর্যন্ত- সবই এই কাতারে পড়ে। বলিউডে কয়দিন পর পর এরকম সিনেমা হয়। ‘চাক দে ইন্ডিয়া’, ‘দাঙ্গাল’, ‘মরদাঙ্গি’, ‘নো ওয়ান কিলড জেসিকা’ এমন শতো শতো ছবির নাম বলা যেতে পারে। বলা বাহুল্য, উইমেন্স ফিল্ম মাত্রই ফেমিনিস্ট ফিল্ম নয়। রেহানা মারিয়াম নূর একই সঙ্গে উইমেন্স ফিল্ম এবং নিঃসন্দেহে ফেমিনিস্ট ফিল্মও বটে। মা-মেয়ের খেলাধুলা বিষয়ক সংলাপের মধ্যেও এই সত্য স্পষ্ট। একজন সচেতন মা, যিনি কন্যাসন্তানকে মেয়ে নয়, বরং মানুষ করে গড়ে তুলতে চান, কেবল তিনিই এভাবে বলতে পারেন, খেলার কোনো ছেলে মেয়ে নেই, খেলা খেলাই।

যথাযথ ডে কেয়ার, স্কুল ট্রান্সপোর্ট এবং নিরাপত্তাবিহীন এই নগরে একজন সিঙ্গেল মাদারের বাচ্চাকে স্কুল থেকে আনা নেওয়া এবং নিজের কর্মজীবন একই সঙ্গে চালিয়ে যাওয়া কতো কঠিন- তা অনেকেই নিজের জীবন দিয়ে জানেন। এই সংগ্রাম করতে করতে একজন নারী কখন রেহানার মতন রাগী, জেদি ও একরোখা হয়ে ওঠেন তা-ও অনেকেই অনুমান করতে পারেন। অবশ্য কেউ কেউ স্বভাবগত ভাবেই রাগী জেদি ও একরোখা হয়ে থাকেন। কিন্তু সেই ব্যক্তিটি নারী হলে তার স্টিগমা বেড়ে যায় শতগুণ। এই মানুষগুলোর মধ্যে থাকা নরম, কোমল এমনকি মানবিক দিকগুলো আর কেউ দেখে না তখন। অ্যানি ও আয়েশার সঙ্গে রেহানা যে প্রবল সহমর্মিতা নিয়ে কথা বলেছেন, সিস্টারহুডের যে শক্তি দেখিয়েছেন, সেসব তলিয়ে যায় তার অসহায় অক্ষম ক্রোধের তলায়।
অনেকেই বলছেন, এমন মানুষকে আদর্শ ধরার বা গ্লোরিফাই করার কিছু নেই। এই সিনেমায় রেহানা মূল চরিত্র হলেও তার নেতিবাচক দিকগুলো লুকানো হয়নি বা আদর্শায়িতও করা হয়নি। সাদের সিনেমা বানানোর স্টাইল প্রসঙ্গে শুরুতে বলেছিলাম- রঙ, ফ্রেম, কাট। কিন্তু একটা কথা বলা হয়নি, যা তার আগের ফিল্মেও দেখা গেছে। চরিত্র চিত্রায়নের ক্ষেত্রে নির্মাতাকে বলা যায় ব্রুটালি অনেস্ট। কাউকে মহান না করার, কাউকে ডিমোনাইজ না করার, মানুষের মধ্যে ভালোমন্দ সব দিক সহই পুরো মানুষটাকে হাজির করার একটা প্রবণতা নির্মাতার মধ্যে রয়েছে। একটা পিস অব আর্ট তখনই গ্রেট হয়ে ওঠে, যখন তাতে এই মানবিকতাটুকু থাকে। লেখার শিরোনামে ‘আরও একটি’ যুক্ত করার কারণও এই। লাইভ ফ্রম ঢাকা দেখে এসেই একটা প্রতিক্রিয়া লিখেছিলাম। দেশ রুপান্তর লেখাটি প্রকাশ করেছিলো। ‘১০০% হালাল ঢাকা’ শিরোনামের সেই লেখায়ও আমি এই নির্মাতাকে সাধুবাদ জানিয়েছিলাম তার সৎসাহসের জন্যই।
তবুও একজন ব্যাড ম্যানারড্ বা শর্ট টেম্পার্ড মহিলাকে মূল চরিত্র করে চলচ্চিত্র নির্মাণ করলে খারাপ জিনিসকে মহান করে তোলার আওয়াজ ওঠে। কিন্তু হায়, জগতে সিরিয়াল কিলার, গ্যাংস্টার আর মাফিয়াদের নিয়ে হাজার হাজার ফিল্ম হয়েছে, হচ্ছে এবং হয়। এমনকি যুগে যুগে পুরুষ পরিচালকরা যৌনকর্মী ও বেশ্যাপল্লী নিয়ে চলচ্চিত্র তৈরি করেছেন ও করছেন। সে সব সিনেমায় যৌনকর্মকে মহান করে তোলা না হলেও, ভিকটিমাইজ করার সঙ্গে সঙ্গে রোম্যান্টিসাইজ করা হয়, গ্ল্যামারাটাইজডও করা হয় যথেষ্টই। তখন তেমন আওয়াজ কিন্তু শোনা যায় না। আফটার অল ইটস আ ম্যান’স ওয়ার্ল্ড।
এবার বলি সবচেয়ে দুর্বল দিকটির কথা। নারীপ্রশ্ন বা নারীবাদ নিয়ে পুরুষের বোঝাবুঝি আর ব্যখ্যা বিশ্লেষণকে সন্দেহ করি- আগেই বলেছি। রেহানাকে হাসপাতালে দেখতে এসে আত্মীয়রা হাউজহোল্ড চরস বা জেন্ডার ডিভিশন অব লেবার নিয়ে যে ধরনের আলাপ আলোচনা করেন, তাকে নারীবাদের প্রথমপাঠ বা ছোটোদের নারীবাদ শিক্ষা ক্লাস বলে মনে হয়েছে। প্রথমত, এক ছবিতে নারীপ্রশ্নের এতো এতো দিক তুলে ধরার কোনো প্রয়োজন ছিলো না, ফোকাসড থাকলেই ভালো হতো। দ্বিতীয়তো, ওই সিকোয়েন্স দিয়ে স্পষ্ট বুঝতে পারা যায় যে, এই ছবির লক্ষ্য নারীবাদের বৈশ্বিক এজেন্ডা, নারী অধিকার ইস্যুর রমরমা বাজার। এ কথা সত্য হলেও এতটা নিরাবরণ এবং অশক্ত উপস্থাপন হতাশাজনক।
সব শেষে বলতে চাই, পুরুষের জগতকে এমন একটা নারীর গল্প উপহার দেওয়ার জন্য রেহানা মরিয়ম নূরের পরিচালক আব্দুল্লাহ মোহাম্মদ সাদকে ধন্যবাদ, যিনি স্পষ্ট উচ্চারণে বলতে পারেন, ভালো মায়ের সার্টিফিকেট পাওয়ার আশা বা পরোয়া তিনি করেন না। মাতৃত্বকে মহান করে তোলার, মাকে মনুষ্যতর, সর্বংসহা, স্নেহ ও মায়ার আধার, সকল অন্যায়ের ঊর্ধ্বে তুলে ধরে তার সময়, শ্রম ও জীবনকে শোষণ করার যে চর্চা পুরুষ নির্মিত এবং পুরুষালী আর্টের, গল্পের, ফিল্মের পাতায় পাতায় স্বর্ণাক্ষরে লেখা রয়েছে, তাদের ওপর শক্ত চপেটাঘাত হিসেবে রেহানার শেষ দৃশ্য ইতিহাসের পাতায় লেখা থাকুক।
*প্রথম প্রকাশ: ৩০ নভেম্বর ২০২১, ফিকশন ফ্যাক্টরি