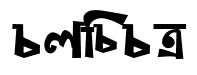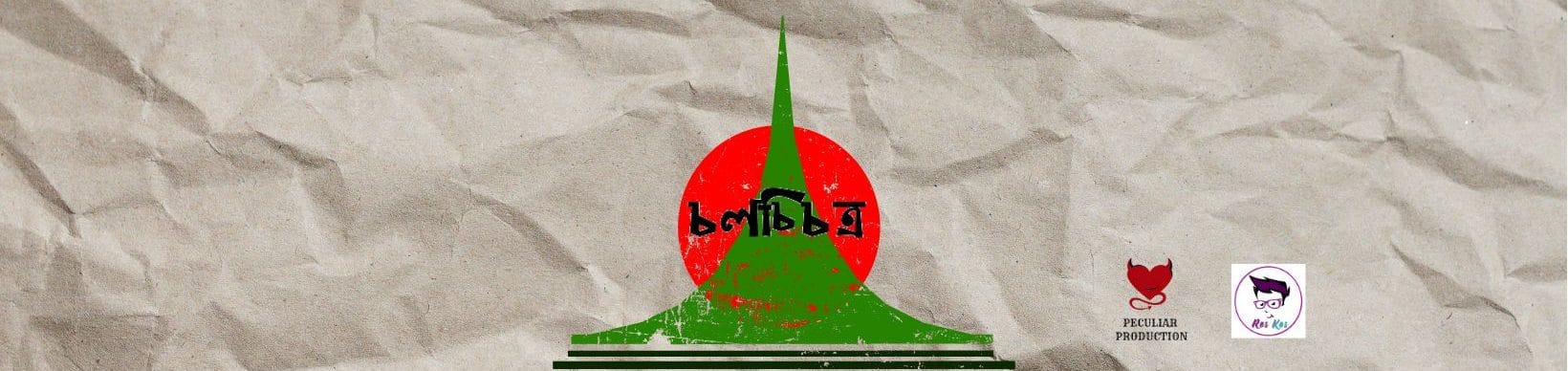“কোন কালে একা হয় নি ক’ জয়ী পুরুষের তরবারি,
প্রেরণা দিয়াছে, শক্তি দিয়াছে বিজয়-লক্ষ্মী নারী।”
(নারী, কাজি নজরুল ইসলাম)
এই বিজয়লক্ষ্মী নিজেই যখন হাতে তরবারি তুলে নিয়ে ঘোড়সওয়ারি হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন রণাঙ্গনে, তখন কি আর তাঁর ভূমিকা কেবল প্রেরণা এবং শক্তি দানেই সীমাবদ্ধ থাকে? ইতিহাস বইয়ের পাতায় যুদ্ধবেশে সজ্জিত ঝাঁসির রাণীর ছবিটা তো আমাদের খুবই পরিচিত। আশ্চর্য এটাই, ১৮৫৭ এর মহাবিদ্রোহে ব্রিটিশ-বিরোধী সম্মুখসমরে আত্মাহুতি দেওয়া সেই বীরাঙ্গনার নামটাও ছিল লক্ষ্মী। দেশনায়ক সুভাষচন্দ্র বসু তাঁর কৈশোরেই প্রবলভাবে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন ঝাঁসির রাণী লক্ষ্মীবাঈ এর বীরত্বপূর্ণ লড়াইয়ের কাহিনি পাঠ করে।


তাই সশস্ত্র সংগ্রামের পথে ভারতের স্বাধীনতা অর্জনের লক্ষ্যে তাঁর নেতৃত্বাধীন আজাদ হিন্দ বাহিনীর নারীযোদ্ধাদের নিয়ে তিনি গড়ে তোলেন রাণী ঝাঁসি বাহিনী। এখানেও এক সমাপতন। এই নারী বাহিনীর অধিনায়কও ছিলেন আর এক লক্ষ্মী। লক্ষ্মী স্বামীনাথন। যুদ্ধপোশাকে সজ্জিত রানী ঝাঁসি বাহিনীর ক্যাপ্টেন লক্ষ্মী ও নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু বীরবিক্রমে পাশাপাশি হেঁটে চলেছেন- এই ছবি আজ সুপরিচিত। কিন্তু, এর পশ্চাৎপটের ইতিহাস সুদীর্ঘ, জটিল ও বর্ণময়। সুভাষচন্দ্রের নারীভাবনা তাঁর অধ্যয়নে, পারিবারিক জীবনে, জাতীয় আন্দোলনের মঞ্চে, ইউরোপের অভিজ্ঞতায় স্তরে স্তরে বিকশিত। আর তার চূড়ান্ত প্রকাশ রানী ঝাঁসি বাহিনীতে।


ইতিহাস জানে, মানুষের চিন্তাকে গড়ে দেয় সময়। সুভাষচন্দ্র যখন বড় হচ্ছেন, সেই সময় বাংলা তথা ভারতের বৌদ্ধিক আকাশ আলোকিত করে রেখেছেন চিরস্মরণীয় নক্ষত্ররা। তাঁদের চিন্তা প্রভাব ফেলেছিল সুভাষের নারীচেতনায়। পূর্বসূরি মনীষীদের মূল্যবোধ ও নারী সম্পর্কে ভাবনাচিন্তা যেমন সুভাষচন্দ্রকে প্রভাবিত করেছিল, তেমনই স্বদেশ ও বিদেশের বিদুষী, মহীয়সী ও বীরাঙ্গনাদের ইতিহাসও তাঁকে প্রেরণা যোগায়। পারিবারিক জীবনে ও বন্ধুবৃত্তে ব্যক্তিত্বময়ী, স্নেহশীলা, বুদ্ধিমতী নারীদের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ও সাহচর্যও সুভাষকে সমগ্র নারীজাতির প্রতি শ্রদ্ধাশীল করে তুলেছিল।
ভুললে চলে না, একজন মনীষীর চিন্তাধারা তাঁর সমকালীন চিন্তাজগতের প্রভাববিযুক্ত নয়। সুভাষের নারীভাবনাকে বোঝার আগে তাই বুঝতে হবে ঊনবিংশ ও বিংশ শতকের ভারতের বৌদ্ধিক প্রেক্ষাপটকে। সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ সরকার তার ঔপনিবেশিক শাসন-কাঠামোকে সুদৃঢ় করার লক্ষ্যেই ভারতের অভ্যন্তরে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রসার ঘটায়। ভারতের শিক্ষিত উচ্চবর্গীয় সম্প্রদায় এই শিক্ষার আলোকপ্রাপ্ত হওয়ার ফলেই সমাজের একটা স্তরে প্রবেশ করে পাশ্চাত্যের দর্শন, আদর্শ ও আধুনিক চিন্তাধারা। ইউরোপীয় জ্ঞান-বিজ্ঞান, যুক্তিবাদ, ব্যক্তিস্বতন্ত্রতা, স্বাধীনতা ও জাতীয়তাবাদের ধারণা ভারত-মননকে স্পর্শ করে। এই নবজাগরণের আলোকস্পর্শ এদেশের একদল দায়িত্ববান মানুষকে মধ্যযুগীয় রক্ষণশীল চিন্তাধারার বিরুদ্ধে প্রতিবাদে সোচ্চার করে তোলে, যার গুরুত্বপূর্ণ প্রকাশ ঘটেছিল নারীভাবনার ক্ষেত্রে। পাশ্চাত্যের ব্যক্তিস্বাধীনতা ও নারীস্বাধীনতা দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে এদেশেও দেখা দেয় নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা।
ভারতীয় নবজাগরণের প্রকৃতি খুব সরল এবং একমাত্রিক নয়। তাকে বুঝতে চাইলে আমাদের একটু চোখ রাখতে হবে ইউরোপীয় রেনেসাঁর গতিপ্রকৃতির দিকেও। ষোড়শ শতাব্দী থেকে ইউরোপে অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে যে সর্বাত্মক পরিবর্তন সাধিত হয়, সেটাই রেনেসাঁ বা নবজাগরণ। এই রেনেসাঁ সামন্তযুগীয় অচলায়তনের বন্ধনদশা ভেঙে উৎপাদন শিল্প, সাহিত্য ও বিজ্ঞানের অগ্রগতির দ্বার খুলে দেওয়ায় নবগঠিত পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থার বিকাশ সহজতর হয়। কিন্তু বহু উন্নতি সত্ত্বেও পুঁজিবাদ তার নিজস্ব নিয়মেই কালক্রমে ‘সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতা’র বাস্তব রূপায়ণে ব্যর্থ হয়ে মুনাফার স্বার্থে ঘটে চলা ক্রমবর্ধমান শোষণের অনিবার্য পরিণতিতে সংকটগ্রস্ত হয়ে পড়ে। এই সংকটগ্রস্ত পুঁজিবাদের চরিত্র তখন আর তার জন্মলগ্নের মতো প্রগতিশীল থাকে না। উপরন্তু শ্রমিক-বিপ্লবের ভয়ে আতঙ্কিত হয়ে সে ধর্মের সঙ্গে, বেশ কিছু পুরাতন প্রতিক্রিয়াশীল ভাবনার সঙ্গে আপস করতে শুরু করে। ইউরোপীয় নবজাগরণের মানবতাবাদী ধারার যখন এই সংশোধিত ও ক্ষয়িষ্ণু অবস্থা, সেই সময় ভারতে নবজাগরণের সূচনা ও বিকাশ পরিলক্ষিত হয়। তাই ভারতীয় রেনেসাঁর মধ্যে ইউরোপীয় রেনেসাঁর সূচনাকালীন বিপ্লবাত্মক এবং পরবর্তী আপসকামী উভয় ধারারই প্রভাব দেখা যায়। ভারতের স্বদেশচেতনা ও নারীভাবনার ক্ষেত্রগুলিও তার ব্যতিক্রম নয়।
তবে একথা ঠিক, অনেক উত্থান-পতন ও বৈচিত্র্য সত্ত্বেও প্রতিটা যুগের একটা নির্দিষ্ট যুগধর্ম থাকে। ঊনবিংশ শতাব্দীর ভারতের সেই যুগধর্ম অনুযায়ীই শিক্ষা, সংস্কৃতি, সাহিত্য, সমাজ, রাজনীতি সবক্ষেত্রেই একটা বিরাট ইতিবাচক পরিবর্তনের হাওয়া এসেছিল। তাই ধর্মসংস্কার, সমাজসংস্কার, স্বাধীনতা আন্দোলন ইত্যাদি সকল মঞ্চেই পৃথক পৃথক সুরে হলেও সে দিন নারীস্বাধীনতার জয়গান শ্রুত হয়েছিল। পাশাপাশি প্রায় সকল স্তরের মানুষের মধ্যেই ব্রিটিশ শাসকের শোষণ ও অত্যাচারের প্রতিবাদে ভারতীয় জাতীয়তাবাদী স্বদেশচেতনাও বিকশিত হয়েছিল। সুভাষচন্দ্রের প্রথম জীবনের নারীভাবনাকে বুঝতে হলে পরিচিত হতে হবে ঊনবিংশ শতাব্দীর ধর্ম ও সমাজ-সংস্কারের আলোয় জন্ম নেওয়া ভারতীয় নারীভাবনার স্বরূপটির সঙ্গে।
ধর্ম-সংস্কারের পথ ধরে ভারতীয় নবজাগরণের ফলিত রূপটি বিকাশ লাভ করায় নবজাগরণের গর্ভজাত ভারতীয় জাতীয়তাবাদও জন্মলগ্ন থেকেই হিন্দু ধর্মভিত্তিক জাতীয়তাবাদ হিসেবে গড়ে ওঠে। হিন্দু পুনরুত্থানবাদী দার্শনিক স্বামী বিবেকানন্দই সর্বপ্রথম ভারতের মাটিতে হিন্দু ধর্মের সংস্কারের পথে জাতীয়তাবাদী জাগরণ এনেছিলেন। এই সংস্কারের লক্ষ্যেই যুগের প্রয়োজনকে স্বীকার করে তিনি নারীস্বাধীনতার ডাক দিয়েছিলেন। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন নারীসমাজের বিকাশ না ঘটলে জাতির অগ্রগতি অবরুদ্ধ থেকে যাবে। তাই তিনি স্পষ্টই ঘোষণা করেন, “ভারতের কল্যাণ স্ত্রী জাতির অভ্যুদয় না হইলে সম্ভাবনা নাই। একপক্ষে পক্ষীর উত্থান সম্ভব নহে।” তা সত্ত্বেও বিবেকানন্দের সমগ্র চিন্তাজগৎ জুড়ে লক্ষণীয় একটা আশ্চর্য টানাপোড়েন। হিন্দুধর্মীয় চিন্তা এবং ইউরোপীয় জ্ঞান ও মানবতাবাদী ধারণার মিলিত ভাবধারায় পরিচালিত হয়েই ভারতের সদ্যজাত জাতীয়তাবাদকে শক্তি জোগানোর জন্য তিনি প্রাচীন ভারতীয় গৌরবকে তুলে ধরেছেন। একদিকে ইউরোপ-আমেরিকার নারী-অগ্রগতি দেখে তিনি চমৎকৃত হয়েছেন, আবার তার পাশাপাশি ভারতের সনাতন হিন্দু ধর্মভিত্তিক সমাজকাঠামোয় নারীজীবনের গৌরবকেও তুলে ধরতে চেয়েছেন। তাই বিবেকানন্দের সম্বোধনে নারী “মা জগদম্বা”, “শক্তি” ইত্যাদি অভিধায় ভূষিত। সীতা-সাবিত্রীই তাঁর আদর্শ। আধ্যাত্মিক স্তরে মহিমান্বিত করেই বিবেকানন্দ ঘরে এবং বাইরে নারীর ক্ষমতাকে বিকশিত করতে চেয়েছিলেন। সুভাষচন্দ্র বাল্য ও কৈশোরে বিবেকানন্দের চিন্তা দ্বারা গভীরভাবে অনুপ্রাণিত ছিলেন।
বিবেকানন্দের আধ্যাত্মিক জীবনের শিক্ষক মানবপ্রেমিক শ্রীরামকৃষ্ণ নারীকে দেবী ও মাতৃরূপে কল্পনা করে মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। যে সময় পারিবারিক, সামাজিক কোনো ক্ষেত্রেই মেয়েদের কোনো অধিকার ছিল না, তখন ধর্মকে আশ্রয় করে হলেও মেয়েদের এই সম্মান ও স্বীকৃতি প্রদান কোনও অংশেই কম গুরুত্বপূর্ণ ছিল না। আবার, হিন্দু ধর্মের সংস্কারের পথে যে জাতীয়তাবাদের জাগরণ এনেছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ, সেই হিন্দুধর্মভিত্তিক জাতীয়তাবাদকে সাহিত্যে জনপ্রিয় করেন বঙ্কিমচন্দ্র। তাই তাঁর “বন্দেমাতরম” এ চিত্রিত দেশমাতৃকার মূর্তি যেন হিন্দুদের আরাধ্যা জগজ্জননী দেবীরই স্পষ্ট প্রতিরূপ। আমাদের দেশের আপসকামী ও আপসহীন উভয় ধারার অধিকাংশ স্বাধীনতা সংগ্রামীই বঙ্কিমচন্দ্রের বন্দেমাতরমকে দেশপ্রেমের বীজমন্ত্র হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। পাশাপাশি বিবেকানন্দর চিন্তাধারা এদেশের জাতীয়তাবাদী সংগ্রামকে প্রভাবিত ও প্রেরণাদায়িত করে। ফলে, ভারতের বৌদ্ধিক চেতনার আকাশে নারীভাবনা ও স্বদেশভাবনার এক সমন্বয় দেখা দেয়, যেখানে নারী, দেবী এবং মাতৃভূমি যেন মিলেমিশে একাকার হয়ে যায়।
জাতীয় আন্দোলনের মঞ্চে বিকশিত হয়ে নতুন রূপ নেয় সুভাষের নারীচেতনা। জাতীয় নেতৃবৃন্দ উপলব্ধি করেছিলেন স্বাধীনতার যুদ্ধে পুরুষের পাশাপাশি নারীদেরও যোগদান করার প্রয়োজন আছে। বিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগেই ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ বিরোধী বয়কট ও স্বদেশী আন্দোলনে নারীদের ব্যাপক অংশগ্রহণ চোখে পড়ে। বিলেতই দ্রব্য বয়কট ও স্বদেশী পণ্যের প্রসার বাংলার সাধারণ মেয়েদের প্রত্যক্ষ সহযোগিতা ছাড়া সম্ভব হত না। চারণকবি মুকুন্দদাস তো বঙ্গনারীদের উদ্দেশ্যেই রেশমি চুড়ি প্রত্যাখ্যান করার ডাক দিলেন। জাতীয় শিক্ষা আন্দোলনেও অগ্রণী ভূমিকা নেন মেয়েরা। শুধুই যোগদানে নয়, নেতৃত্বদানেও এগিয়ে ছিলেন তাঁরা।
রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী বঙ্গভঙ্গ কার্যকরী হওয়ার দিন যে অরন্ধন ও উপবাসের ডাক দিয়েছিলেন, সরলাদেবী চৌধুরানি, গিরিবালা দেবী, অবলা বসু, হেমাঙ্গিনী দাস, কুমুদিনী মিত্র, লীলাবতী মিত্র, সুবালা আচার্য, নির্মলা সরকার প্রমুখের নেতৃত্বে বাংলার আপামর নারীরা তা পালন করেন। স্বদেশী কর্মসূচীকে শক্তি জোগাতে স্বর্ণকুমারী দেবী সখীসমিতি, সরলা দেবী চৌধুরাণী লক্ষ্মীর ভাণ্ডার প্রতিষ্ঠা করেন।
গান্ধিজির নেতৃত্বাধীন অসহযোগ ও আইন অমান্য আন্দোলনে নারীরা বীরত্বপূর্ণ অবদান রেখেছিলেন। ১৯২১ সালে অসহযোগ আন্দোলনের সময় দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের নির্দেশে বিদেশী দ্রব্য পিকেটিং ও খদ্দর ফেরি করার কাজে বাসন্তী দেবীর নেতৃত্বে উর্মিলা দেবী ও সুনীতি দেবী যোগদান করেন। প্রকাশ্য রাজপথে আইন অমান্য করে তাঁরা গ্রেপ্তার বরণও করেন। এই গ্রেপ্তারের প্রতিক্রিয়ায় ভারতের জনমানসে তীব্র প্রতিবাদের জাগরণ দেখা যায়। আইন অমান্য আন্দোলনে কলকাতা ছাড়াও বোম্বাই, দিল্লি, এলাহাবাদ, লক্ষ্ণৌ, লাহোর প্রভৃতি শহরে নারী-আন্দোলন সংগঠিত হয়।
সশস্ত্র সংগ্রামে বিশ্বাসী সুভাষচন্দ্র বসু গান্ধিজির অহিংস নীতিতে আস্থাশীল ছিলেন না। তিনি সারা দেশ জুড়ে ব্রিটিশ বিরোধী আপসহীন সংগ্রাম গড়ে তোলার পক্ষপাতী ছিলেন। কিন্তু, মতপার্থক্য সত্ত্বেও গান্ধিজির গড়ে তোলা গণজাগরণ যে নারীজাগরণের জন্ম দিয়ে দিয়েছিল, তাকেই কাজে লাগিয়ে সুভাষচন্দ্র বিরাট গণ-অভ্যুত্থান গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। জাতীয় আন্দোলনের দুইটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ হিসেবে নারী-আন্দোলন ও যুব-আন্দোলনকে তিনি শক্তিশালী করে তুলতে চান। সাইমন-কমিশন বিরোধী বয়কট আন্দোলনের সময় সুভাষচন্দ্র যে আলোড়ন মেয়েদের মধ্যে সৃষ্টি করেন, তার প্রেরণাতেই ১৯২৮ সালে গড়ে ওঠে ছাত্রীসঙ্ঘ, যা ক্রমেই কলকাতার নারী-বিপ্লবী সংগঠনের প্রাণকেন্দ্র হয়ে ওঠে। এই সংগঠনের সক্রিয় সদস্য ছিলেন বীণা দাস, কমলা দাশগুপ্ত, প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার, কল্পনা দত্ত, ইলা সেন, সুহাসিনী গাঙ্গুলি, সুলতা কর প্রমুখ বিপ্লবী।
১৯২৮ এর কলকাতা কংগ্রেসের অধিবেশনে সুভাষচন্দ্র গড়ে তোলেন স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী, যার একটি অংশ ছিল নারীবাহিনী। কংগ্রেস সভাপতি মতিলাল নেহেরুকে নিয়ে যে শোভাযাত্রা গঠিত হয়েছিল, সেখানেই ভারতবর্ষের ইতিহাসে প্রথমবার প্রকাশ্য রাস্তায় নারীরা পুরুষের সঙ্গে সামরিক কায়দায় কুচকাওয়াজ করেন। সেদিনের এই কুচকাওয়াজের শব্দেই ভারতের নারীভাবনার নতুন যুগের পদধ্বনি মিশে ছিল। সুভাষচন্দ্রের এই পদক্ষেপেই নিহিত ছিল ভবিষ্যতের আজাদ হিন্দ ফৌজ এবং রাণী ঝাঁসি বাহিনী গঠনের অনুপ্রেরণা।
১৯৩৩ সাল থেকে ইউরোপে থাকার ফলে সুভাষচন্দ্র বসু খুব কাছ থেকেই সংস্পর্শে আসেন পাশ্চাত্যের বিভিন্ন ধারার সমাজতান্ত্রিক মতবাদের, যার প্রভাবে তাঁর চেতনায় ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন ও নারীমুক্তিভাবনা এক নতুন মোড় নেয়। আন্তর্জাতিক মঞ্চে তিনি ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে নারীজাতির ভূমিকা বিষয়ক ভাবনাকে উপস্থাপন করেন ভিয়েনা কল ক্লাবের বক্তৃতায় ১৯৩৫ সালে। ওই বছরই জেনেভায় নারীদের আন্তর্জাতিক লিগের ব্যাপারে সুভাষচন্দ্র মতামত রাখেন। ১৯৩৮এ যখন সুভাষচন্দ্র বসু ভারতে ফিরলেন, তখন তিনি সম্পূর্ণতই সমাজতন্ত্রের ভাবাদর্শে উদ্বুদ্ধ এক মুক্তিসংগ্রামী, যিনি স্পষ্ট ঘোষণা করছেন, স্বাধীন ভারতের সামাজিক পুনর্গঠন কিন্তু সমাজতান্ত্রিক ধারাতেই হবে। এই সমাজতান্ত্রিক সাম্যের আদর্শ বুকে নিয়েই ভারতের স্বাধীনতার লক্ষ্যে তিনি তাঁর ভবিষ্যতের আজাদ হিন্দ বাহিনীকে নির্মাণ করেছিলেন।
ভারতের বাইরে থেকে সামরিক আঘাতে স্বাধীনতা অর্জনের পরিকল্পনায় ১৯৪১ সালের ১৭ জানুয়ারি যে দুঃসাহসিক অভিযানের সূচনা করলেন সুভাষচন্দ্র, তারই পূর্ণতা প্রাপ্তি ১৯৪৩ সালে ২৫ আগস্ট আনুষ্ঠানিকভাবে রাসবিহারী বসুর হাত থেকে আজাদ হিন্দ বাহিনীর দায়িত্বগ্রহণে। দায়িত্বলাভের পর নেতাজি গঠন করেন এই বাহিনীর চারটি ব্রিগেড। গান্ধি ব্রিগেড, নেহেরু ব্রিগেড ও সুভাষ ব্রিগেডের পাশাপাশি লক্ষ্মী স্বামীনাথনের নেতৃত্বে নারীদের নিয়ে গঠিত হয় রাণী ঝাঁসি ব্রিগেড। এই বাহিনীর নারীযোদ্ধারা পুরুষের মতোই যুদ্ধপোশাকে সজ্জিত হয়ে অস্ত্র হাতে তুলে নিয়েছিলেন। ইতিপূর্বে রাসবিহারী বসুর নেতৃত্বাধীন ইন্ডিয়ান ইন্ডিপেন্ডেন্স লিগের মহিলা শাখা সমাজকল্যাণমূলক কাজে রত ছিল। এই লিগের হেড কোয়ার্টারের নারী বিভাগের সম্পাদিকা লক্ষ্মী স্বামীনাথনও জনসেবামূলক চিকিৎসাকার্যে নিযুক্ত ছিলেন।


রাণী ঝাঁসি বাহিনীর নারীদের সামরিক ও অসামরিক দুরকম ভূমিকাই পালন করতে হত। বাহিনীর রেড ক্রস ইউনিটের কাজ ছিল যুদ্ধে আহত অন্যান্য সৈন্যদের সেবা করা। মেয়েদের জন্য ছিল আলাদা শিক্ষার ব্যবস্থা। ছিল সুনির্দিষ্ট পাঠক্রম, অস্ত্রচালনা প্রশিক্ষণ এবং গেরিলা যুদ্ধের প্রশিক্ষণও। নেতাজির নির্দেশে ও স্বামীনাথনের নেতৃত্বে অত্যন্ত যুক্তিনিষ্ঠ, সুপরিকল্পিত ও বাস্তবসম্মত পথেই এই বাহিনীর ক্রিয়াকলাপ নির্ধারিত হয়েছিল। দঃ পূঃ এশিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলের বালিকা থেকে বৃদ্ধা সর্বস্তরের নারীরা এই বাহিনীতে যোগদান করেন, যাঁদের ভাষা ও ধর্ম আলাদা। কিন্তু, যুদ্ধক্ষেত্রে তাঁরা এক ও অভিন্ন আত্মা। আজাদ হিন্দ বাহিনী ইম্ফল দখল করার পর বার্মায় অবস্থিত রাণী ঝাঁসি বাহিনী যুদ্ধক্ষেত্রে অগ্রসর হবে, এমনটাই নেতাজির পরিকল্পনা ছিল। কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জাপানের আত্মসমর্পণের ফলে যুদ্ধের মোড় ঘুরে যাওয়ায় আজাদ হিন্দ ফৌজকে পশ্চাদপসারণ করতে হয়। তখন যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হওয়া রাণী ঝাঁসি বাহিনী নেয় ফিরে আসা আহত সৈন্যদের পরিচর্যার দায়িত্ব। বহুমুখী দক্ষতার পরিচয় দিয়ে আজাদ হিন্দ ফৌজের ঝাঁসির রাণী ব্রিগেডের নারীরা ভারতের স্বাধীনতার জন্য নিজেদের সবটুকু শক্তি ও আবেগ উজাড় করে দিয়েছিলেন। এই পর্যায়ে নারীরা আর অলৌকিক কোনো দেবী হিসেবে কল্পিত নন। পুরুষ মুক্তিযোদ্ধাদের প্রেরণাদায়িনী ও সহযোগিনী মাতা বা ভগিনী হিসেবে বর্ণিতও নন। তাঁরা শুধুই সশস্ত্র, প্রশিক্ষিত, বীর মুক্তিসেনানী। পুরুষের সঙ্গে কোনো তুলনায় নয়, ভারতের স্বাধীনতার লক্ষ্যে আত্মনিয়োজিত সৈনিক হিসেবে তাঁরা নিজস্ব ভূমিকাতেই চিরস্মরণীয়।
নবজাগরণ নারীর যে সমানাধিকার প্রতিষ্ঠার ডাক দিয়েছিল, স্বাধীনতা সংগ্রামের ময়দানে ভারতের নারীর সেই সমানাধিকার প্রাপ্তিরই ফলিত রূপটি প্রত্যক্ষ হয়েছিল। আবার নেতাজি সুভাষচন্দ্রের মতো সমাজতান্ত্রিক আদর্শে উদ্বুদ্ধ মুক্তিসেনানায়ক প্রমাণ করেছিলেন, প্রকৃত সাম্য লড়াইয়ের ময়দানেই গড়ে উঠতে পারে। শেখাতে চেয়েছিলেন, স্বদেশমুক্তি এবং নারীস্বাধীনতা তথা মানবমুক্তি অর্জনের লড়াইটা অভিন্ন। এটাই সুভাষচন্দ্রের নারীভাবনার চূড়ান্ত ও পরিণত রূপ।
তথ্যসূত্র
১) অলোক রায়, গৌতম নিয়োগী (সম্পা), উনিশ শতকের বাংলা, পারুল প্রকাশনী, কলকাতা, ২০১১।
২) ড. রত্না ঘোষ, সুভাষচন্দ্রের নারীচেতনা ও রাণী ঝাঁসি বাহিনী, নেতাজী ভাবনা মঞ্চ, কলকাতা, শারদীয়া ১৪২৮ বঙ্গাব্দ।
৩) দিলীপ সাহা, ‘নেতাজী সুভাষ ও আজাদ হিন্দ ফৌজ’, কোরক সাহিত্য পত্রিকা ১২৫ তম জন্মবর্ষে সুভাষচন্দ্র বসু, স. তাপস ভৌমিক, জানুয়ারি-এপ্রিল ২০২২, কলকাতা, ২০২২।
৪) ধনঞ্জয় ঘোষাল (সম্পা), নবচেতনায় বঙ্গনারী প্রাক স্বাধীনতা পর্ব, আশাদীপ, কলকাতা, ২০১৫।
৫) লক্ষ্মী সেহগল, একটি বিপ্লবী জীবন, অনু. আরতি গঙ্গোপাধ্যায়, উপমা, ১৯১৯।
৬) শৈলেশ দে, আমি সুভাষ বলছি, সং. অখণ্ড সংস্করণ, বিশ্ববাণী প্রকাশনী, ১৯৮৫।
৭) সব্যসাচী চট্টোপাধ্যায়, ‘দেশের মুক্তি সংগ্রামে নারী : একটি অসম্পূর্ণ ইতিহাস’, ঋদ্ধি পত্রিকা স্বাধীনতা সংখ্যা, প্রথম পর্ব, স. তন্ময় ভট্টাচার্য, ভাটপাড়া, ২০২১।
৮) সৌমেন বসু, মানব বেরা (সম্পা), অনন্য দেশনায়ক, বিপ্লবী জনমত প্রকাশনা, মেদিনীপুর, ২০২১।