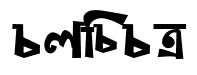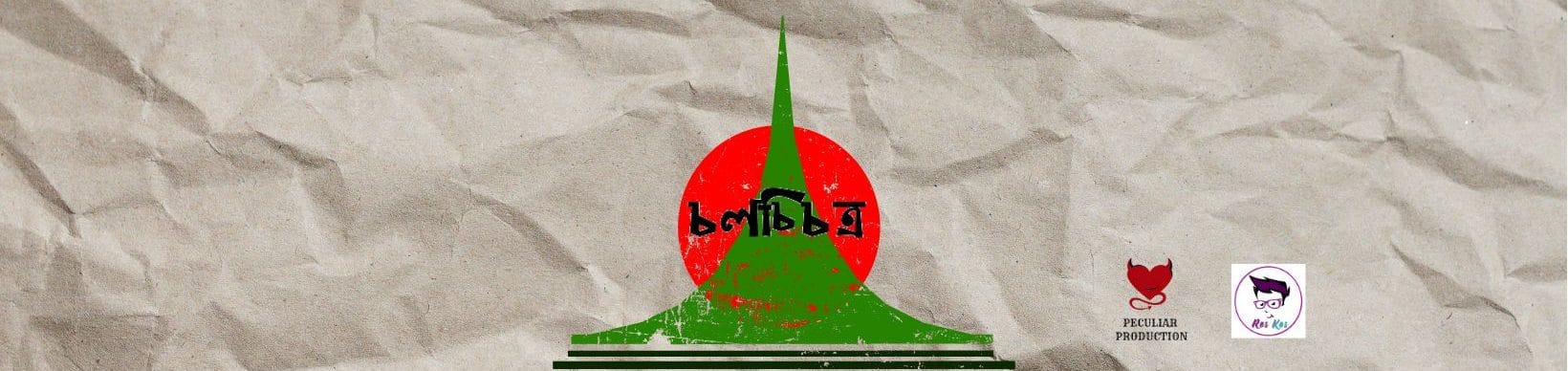বাংলা সিনেমা, যা একসময় বিশ্ব চলচ্চিত্রের মানচিত্রে তার নিজস্ব পরিচিতি এবং মহত্ব প্রতিষ্ঠা করেছিল, দীর্ঘকাল ধরে বাণিজ্যিকভাবে এবং শিল্পগতভাবে কিছুটা সংকটে ছিল। ১৯৯০ এবং ২০০০-এর দশকে বাণিজ্যিক সিনেমার আধিক্য, নির্মাণের মানের অবনতি, এবং অন্যান্য রাজ্যের চলচ্চিত্রের প্রভাবে বাংলা সিনেমা অনেকটা পিছিয়ে পড়ে। তবে, গত এক দশকে বাংলা সিনেমার প্রতি বিশেষ এক ধরনের “রিভাইভাল” বা “কমব্যাক” ট্রেন্ড লক্ষ্য করা যাচ্ছে। একদিকে যেমন প্রযুক্তির উন্নতি এবং বিদেশি প্রভাবের মধ্যে বাংলা সিনেমা আধুনিক যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে, তেমনি অন্যদিকে বেশ কিছু নির্মাতা এমন কিছু ছবি উপস্থাপন করছেন, যা আবার সেই অতীত গৌরব ফিরিয়ে আনার ইঙ্গিত দেয়।
এই প্রবন্ধে আমরা বিশ্লেষণ করব বাংলা সিনেমায় এই কথিত “রিভাইভাল” বা “কমব্যাক” ট্রেন্ডের প্রেক্ষাপট, বর্তমান বাংলা সিনেমার অবস্থা এবং একে সত্যিই কি “উত্থান” বলা যায়, সে প্রশ্নের উত্তর। আমরা দেখতে চেষ্টা করব এই পরিবর্তনের কারণ, এর গভীরতা এবং ভবিষ্যত সম্ভাবনা কেমন হতে পারে।
১. বাংলা সিনেমার গতিপথ: সংকটকাল থেকে আশার আলো
বাংলা সিনেমার ইতিহাস একদিকে যেমন সমৃদ্ধ, তেমনি একসময় তা সংকটে পড়ে। ১৯৫০-৬০-এর দশক থেকে শুরু করে ১৯৮০-৯০ এর দশক পর্যন্ত, বাংলা চলচ্চিত্র ছিল বিশ্ব চলচ্চিত্রে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। সত্যজিৎ রায়, মৃণাল সেন, ঋত্বিক ঘটক, তপন সিংহ, হুমায়ূন আহমেদ—এইসব নির্মাতারা বাংলা চলচ্চিত্রের এক নতুন দিগন্ত খুলে দেন, যা শুধুমাত্র ভারতীয় নয়, আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র জগতে প্রভাব ফেলেছিল। কিন্তু ১৯৯০-এর দশক থেকে বাংলা চলচ্চিত্রের চিত্র বদলে যায়।
বাণিজ্যিক সিনেমার দিকে ঝোঁক, কম বাজেটে তৈরি হত বহু ছবি, যা মূলত বিনোদনমূলক এবং সস্তা নান্দনিকতার দিকে ঝুঁকেছিল। চলচ্চিত্র নির্মাতারা আর সেই চিন্তাভাবনা অনুসরণ করেননি যা সত্যজিৎ রায় বা ঋত্বিক ঘটক করেছিলেন। অন্যদিকে, কলাকৌশল এবং চিন্তার অভাবের কারণে বাংলা সিনেমার আগের ঐতিহ্যগত শ্রেণি চূড়ান্ত সংকটে চলে যায়। ২০০০-এর দশকে, বাংলা সিনেমার নির্মাণের মানের অবনতির পাশাপাশি, বলিউড এবং দক্ষিণী সিনেমার আধিপত্য বাড়তে থাকে। কলকাতা, যেটি এক সময় চলচ্চিত্রের প্রাচীনতম শিল্পকেন্দ্র ছিল, সেখানে সিনেমার বাজারও দিনদিন সংকুচিত হতে থাকে।
২. রিভাইভাল বা কমব্যাক ট্রেন্ড: সত্যি কি পরিবর্তন?
গত এক দশকে কিছু সিনেমা আবার বাংলা সিনেমার ঐতিহ্য ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করেছে। ২০১০-এর পর বাংলা সিনেমায় যে “রিভাইভাল” ট্রেন্ড শুরু হয়েছে, তার মধ্যে কিছু সিনেমা মুক্তি পায়, যা নতুন প্রজন্মের নির্মাতারা তৈরি করেন। এগুলোর মধ্যে “বিস্বাদ”, “বায়োস্কোপ”, “ভুবন সোম”, “রাজারহাট”, “পারমিতা” প্রভৃতি চলচ্চিত্র বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এগুলি কিছুটা শিল্পীসত্তা এবং গল্পের নতুন দৃষ্টিকোণকে তুলে ধরে। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, এসব ছবির একক প্রচেষ্টার মাধ্যমে বাংলা সিনেমার সত্যিকারের “রিভাইভাল” ঘটছে কি না।
যতই এই পরিবর্তন লক্ষণীয় হোক না কেন, কিছু নির্মাণগত এবং বাজারভিত্তিক সীমাবদ্ধতা থেকেই যাচ্ছে। অধিকাংশ নতুন ছবি এখনও বাণিজ্যিক দিক থেকে মুনাফা অর্জনে বেশি মনোযোগী, এবং সেগুলোর মধ্যে পূর্ণাঙ্গ শিল্পীসত্তার প্রতিফলন পাওয়া যায় না। বিশেষ করে, বাংলা সিনেমায় আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার বা দর্শককে টানার জন্য ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মের কার্যক্রম যত বৃদ্ধি পেয়েছে, ততই গল্পের মৌলিকতা, সৃজনশীলতা এবং সাংস্কৃতিক গভীরতার দিকে বেশি মনোযোগ দেওয়া হচ্ছে না।
৩. প্রযুক্তির প্রভাব: ডিজিটাল বিপ্লব
একটি প্রধান কারণ যা “রিভাইভাল” বা “কমব্যাক” ট্রেন্ডের জন্য সহায়ক, তা হলো আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার। ২০১০-এর পর বাংলায় ডিজিটাল সিনেমা ও ভিডিও প্রযুক্তির ব্যবহার বেড়ে গেছে। ডিজিটাল ক্যামেরা, কম্পিউটার গ্রাফিক্স, এবং নতুন প্রযুক্তির মাধ্যমে সিনেমার প্রযোজনা এবং প্রকাশের খরচ অনেক কমেছে। এর ফলে, চলচ্চিত্র নির্মাতারা নতুন ধরনের গল্প, সাহসী থিম এবং অভিনয়ের জন্য আরও বেশি সুযোগ পাচ্ছেন। পাশাপাশি, জনপ্রিয় ভিডিও স্ট্রিমিং প্ল্যাটফর্ম (যেমন Netflix, Amazon Prime, Hotstar) নতুন ধরনের কনটেন্টের জন্য একটি প্ল্যাটফর্ম সরবরাহ করছে, যা বাংলা সিনেমাকে আন্তর্জাতিক দর্শকের কাছে পৌঁছানোর নতুন পথ খুলে দিয়েছে।
উদাহরণ হিসেবে বলা যেতে পারে “ম্যাজিক”, “দ্য জঙ্গল বুক”, “ক্রিসক্রস” এই ধরনের চলচ্চিত্র, যেগুলো মূলত আধুনিক প্রযুক্তি ও সৃজনশীলতার সংমিশ্রণ। তবে, প্রযুক্তির আগমন শুধুমাত্র একমাত্র কারণ নয়। সিনেমা তৈরির মান, গল্পের ধরণ এবং চরিত্রের গভীরতা এগুলোও যথেষ্ট গুরুত্ব বহন করে।
৪. নতুন প্রজন্মের নির্মাতাদের অবদান
নতুন প্রজন্মের নির্মাতারা, যারা ২০১০-এর পর বাংলা সিনেমার জন্য গুরুত্বপূর্ণ কাজ করেছেন, তাদের সৃষ্টির মধ্যে প্রকৃতপক্ষে একটি শিল্পীসত্তা প্রকাশিত হয়েছে। সৃজিত মুখার্জি, অরিন্দম শীল, শুভজিত মুদি, মৈনাক ভৌমিক, কৌশিক গাঙ্গুলি প্রমুখ নির্মাতারা বাংলা সিনেমাকে নতুন একটি সৃজনশীল স্তরে নিয়ে গেছেন।
যেমন “বাহুবলী” বা “হিন্দি মিডিয়াম”-এর মতো ছবিগুলি যখন বড় পরিসরে দর্শকদের মনোযোগ আকর্ষণ করেছিল, ঠিক তেমনি “বিজয়া”, “যমুনা ধাকুর” এবং “মিসিং” এর মতো ছবিগুলো একটি নতুন দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে দর্শকের কাছে পৌঁছেছে। এই নির্মাতারা সাধারণত বাস্তব জীবন, মনস্তাত্ত্বিক সমস্যা, এবং সমাজের গভীর অন্ধকার দিকগুলি প্রাধান্য দেন, এবং তাদের কাজ কেবল শুধু বিনোদন নয়, বরং চিন্তার খোরাকও সরবরাহ করে।
৫. প্ল্যাটফর্ম এবং বিতরণ: নতুন দিগন্ত
ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মের বিকাশ বাংলা সিনেমার জন্য একটি নতুন দিগন্ত খুলে দিয়েছে। “হইচই”, “অমাজন প্রাইম ভিডিও”, “নেটফ্লিক্স”-এর মাধ্যমে বাংলা সিনেমা নতুন এক বৈশ্বিক বাজার পেতে শুরু করেছে। চলচ্চিত্র নির্মাতারা এখন শুধুমাত্র স্থানীয় বা দেশীয় বাজারের প্রতি মনোযোগী নন, তারা আন্তর্জাতিক দর্শককের সামনে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার সুযোগ পাচ্ছেন। এই বিপ্লব বাংলা সিনেমার একটি শক্তিশালী দিক হিসেবে কাজ করছে। কিছু নির্মাতা যেমন শুভ্রজিৎ মিত্র, সৃজিত মুখার্জি নিজের কাজের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বাংলা সিনেমার একটি নতুন চেহারা উপস্থাপন করেছেন।
৬. বাংলা সিনেমার জন্য ভবিষ্যতের চ্যালেঞ্জ
যদিও “রিভাইভাল” বা “কমব্যাক” ট্রেন্ড খুবই আশাপ্রদ, তবে বাংলা সিনেমার ভবিষ্যতকে আরও শাণিত করতে বেশ কিছু চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে হবে। প্রথমত, গল্পের মৌলিকতা এবং চরিত্রের গভীরতা বজায় রাখতে হবে। দর্শকরা শুধুমাত্র সস্তা বিনোদনের দিকে ঝুঁকবে না, যদি না তাদেরকে একটি শক্তিশালী গল্প এবং ভাবনা উপহার দেয়া হয়। দ্বিতীয়ত, আন্তর্জাতিক মানের প্রযুক্তি এবং বিশেষ দক্ষতার ব্যবহারকে আরও ভালোভাবে কাজে লাগাতে হবে। তৃতীয়ত, সমালোচকদের এবং দর্শকদের জন্য একটি শক্তিশালী সাংস্কৃতিক ভিত্তি তৈরি করতে হবে, যা বাংলা সিনেমাকে আগামী দিনে একটি নির্দিষ্ট পথের দিশা দেখাতে সাহায্য করবে।
বাংলা সিনেমায় যেই কথিত “রিভাইভাল” বা “কমব্যাক” ট্রেন্ড দেখা যাচ্ছে, তা নিঃসন্দেহে একটি আশাপ্রদ লক্ষণ। এই ট্রেন্ডের মধ্যে সৃজনশীলতা, নতুন চিন্তা, এবং প্রযুক্তির ব্যবহার নিয়ে আরও বিকাশের সুযোগ রয়েছে। তবে, বাংলা সিনেমার পূর্ণাঙ্গ উত্থান তখনই সম্ভব হবে, যখন নির্মাতারা শুধুমাত্র শিল্প বা বাণিজ্যিক চিন্তাভাবনা নয়, একসঙ্গে দর্শকদের মনোযোগ আকর্ষণকারী গভীর ও গুরুত্বপূর্ণ গল্পগুলি তুলে ধরবেন। “রিভাইভাল” কথাটি আসলেই পূর্ণাঙ্গভাবে বাংলা সিনেমার অবস্থা নয়, বরং এটি একটি সম্ভাবনার সূচনা—যা আগামী দিনে আরও শক্তিশালী এবং গভীর বাংলা চলচ্চিত্র নির্মাণের দিকে নিয়ে যেতে পারে।